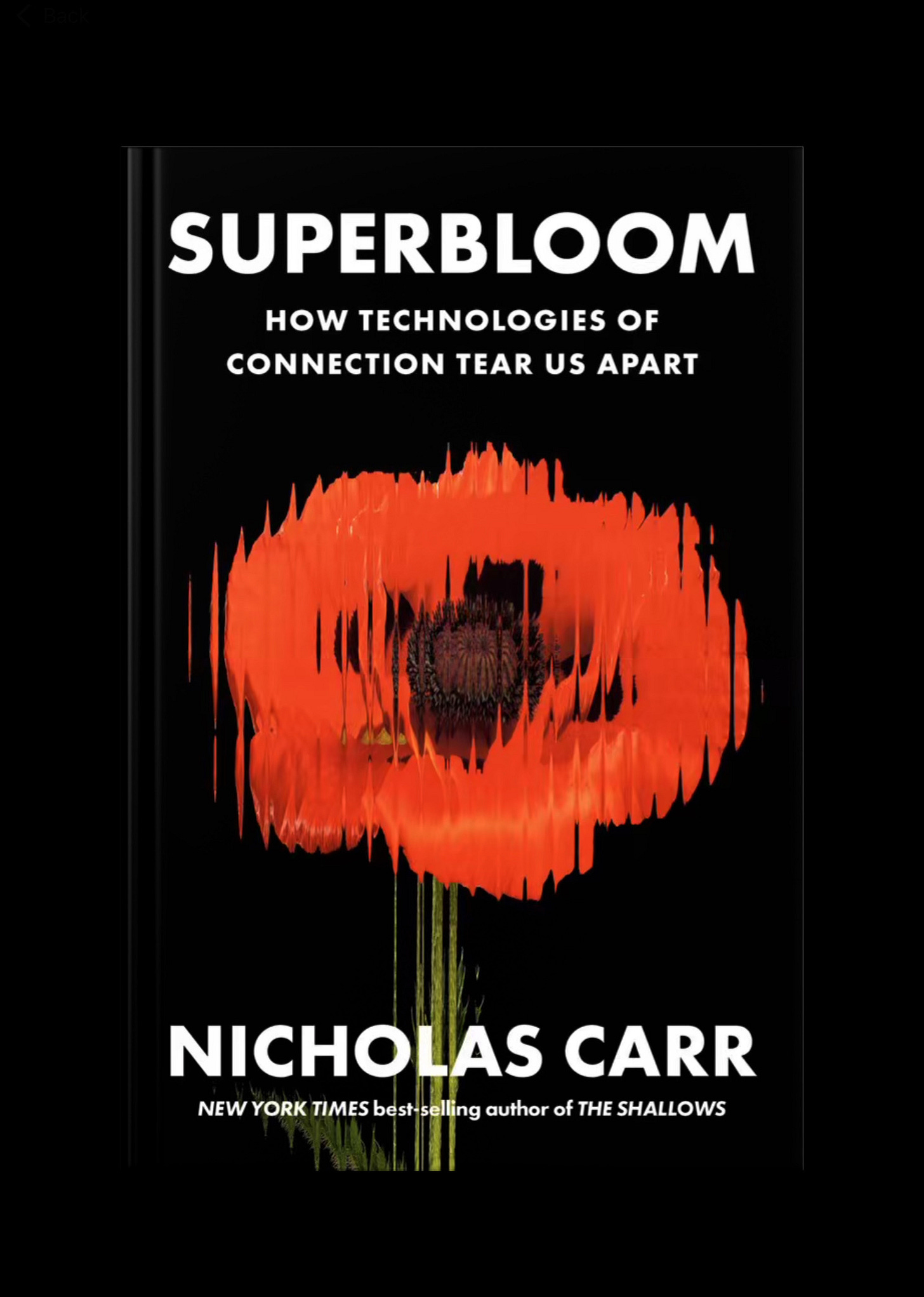সুপারব্লুম: সংযোগের সুতোয় বাঁধা বিপর্যয়
সেই যে এক কালে বাবার হাতে চুড়ি পরা হত, এখন আমরা নিজেরাই মাথায় দোল পরিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছি ডিজিটাল ফুলবাগানে। আর ফল কী? ইনস্টাগ্রামে পপি-সেলফি। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াকার ক্যানিয়নে ফোটে এক দুর্দান্ত কমলা রঙের সুপারব্লুম—ভেবেছিলাম প্রকৃতির প্রেমিকেরা খুশি হবে। কিন্তু প্রেমিকেরা এল না, এল ‘ইনফ্লুয়েন্সার’। মোবাইল ক্যামেরা হাতে এক ২৪ বছরের ডিজিটাল দেবী, দুটো পপ…