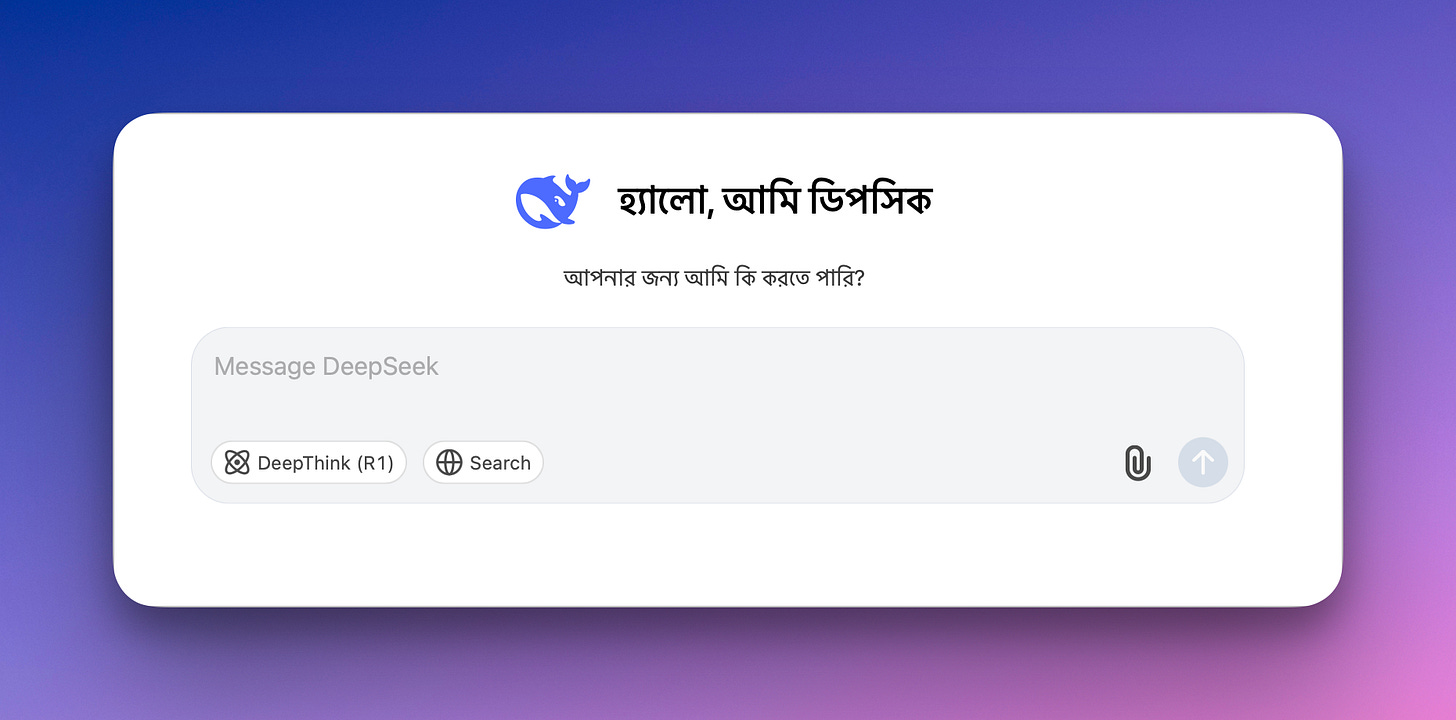DeepSeek এবং আমেরিকান উদ্ভাবন: আমার দুটি কথা
আমেরিকান টেক জায়ান্টরা নিজেদের বিশালত্বের ভারে ধীরগতির হয়ে পড়েছে। তারা এখন উদ্ভাবনের চেয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও লাভ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত।
গত সপ্তাহের শেষ দিকে, কম পরিচিত চীনা এআই স্টার্টআপ DeepSeek দাবি করেছে যে তারা আমেরিকার বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর চেয়েও উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করেছে, তাও অনেক কম খরচে—অথচ তাদের কাছে মার্কিন উন্নত চিপ প্রযুক্তির সুবিধা নেই। তাদের এই দাবিকে অনেকেই অবিশ্বাস্য মনে করলেও, প্রযুক্তির দুনিয়ায় অভাবনীয় ঘটনা যে প্রায়ই ঘটে, সেটিও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষত আজকের দিনে, যখন জ্ঞান, ডেটা, আর মূলধনের সংস্থান আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সহজলভ্য, তখন স্বল্প পরিচিত কোনো স্টার্টআপ যে বড় প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে, DeepSeek তাদের প্রযুক্তি “ওপেন সোর্স” করে দিয়েছে—অর্থাৎ, সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিক করার ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের ঘোষণা। শুধু সফটওয়্যারই নয়, জ্ঞানের প্রবাহও এখন উন্মুক্ত। এই মুক্ত প্রবাহের ফলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল কিংবা স্বতন্ত্র গবেষকরা দ্রুত কিছু অভিনব সমাধান বা পণ্য তৈরি করে ফেলতে পারেন, যা বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আর বিপুল বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল নয়।
আমেরিকান টেক জায়ান্টরা নিজেদের বিশালত্বের ভারে ধীরগতি হয়ে পড়েছে। তারা এখন উদ্ভাবনের চেয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও লাভ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। নতুন কিছু তৈরির বদলে, তারা মূলত ছোটখাটো আপগ্রেডেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। একসময় যেসব কোম্পানি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্ভাবন দিয়ে বাজার কাঁপিয়েছিল, আজ তারা অপ্রতিরোধ্য হওয়ার দরুন রক্ষণশীল নীতিতে আটকে গেছে। তারা এমন সব পণ্য কিংবা সেবা চালু করে যা মূলত একটি সীমিত কৌশলগত গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খায়—যেন বিদ্যমান বাজার ধরে রাখাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।
অপরদিকে, চীনের প্রযুক্তি খাত একে অপরের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। উদ্যোক্তারা জানেন, বাজার দখলের জন্য সেখানে মাত্র কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানের জায়গা নেই—বরং অগণিত স্টার্টআপ একসঙ্গে বাজারের আকাশসীমাকে বড় করে তুলছে। DeepSeek-এর মতো কোম্পানির উত্থান সেটাই প্রমাণ করে। এ কারণেই চীন কেবল এআই-এ নয়, বৈদ্যুতিক যান, ব্যাটারি, এমনকি TikTok-এর মতো নানা ক্ষেত্রে চমকপ্রদ নতুনত্ব আনতে সক্ষম হয়েছে। এই তীব্র প্রতিযোগিতাই তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
লিনা খান, বাইডেন প্রশাসনের ফেডারেল ট্রেড কমিশনের প্রধান, গত মার্চে ঠিকই বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র শুধু "জাতীয় পুঁজিপতি" তৈরি করে প্রযুক্তির শীর্ষে থাকতে পারবে না। আজকাল বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর একচেটিয়া বাজার দখলকে রক্ষা করার জন্য প্রায়ই "জাতীয় পুঁজিপতি" যুক্তি তুলে ধরা হয়। তাদের দাবি, এই একচেটিয়া দখল ভেঙে দিলে উদ্ভাবন দুর্বল হয়ে পড়বে, ফলে চীনের মতো দেশগুলো সহজেই বাজার দখল করে নিবে। কিন্তু আসলে, উদ্ভাবন কখনোই একচেটিয়া শক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এটি বিকাশ লাভ করে প্রতিযোগিতার বাতাবরণে, যেখানে চ্যালেঞ্জ আর সীমাবদ্ধতা নতুন কিছু করে দেখানোর প্রেরণা জোগায়।
এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আমরা দেখতে পারি। বড় বড় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান মূলত আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে যায়, যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা থাকে খুবই কম। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (R&D) নিয়ে তারা বরং ভারী বাজেট বরাদ্দ রাখলেও, চূড়ান্ত ফলাফলে প্রায়ই দেখা যায় প্রকৃত বৈপ্লবিক অগ্রগতি আসছে অন্য কোনো ‘হাংরি’ ছোট প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে। যুক্তরাষ্ট্র যে প্রযুক্তিতে সামনের সারিতে ছিল, তা এসেছে উদ্ভাবনের গতিময়তার কারণে—বড় একচেটিয়া দৌরাত্ম্যের কারণে নয়।
এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এগোনো উচিত? সামনে এগোতে হলে আমাদের একচেটিয়া সংস্থাগুলোকে সুরক্ষিত করা নয়, বরং উদ্ভাবনকে সুরক্ষিত করা দরকার। প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়, যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানই নিজেদের ‘অনন্য’ ভাবতে না পারে, বরং প্রতিদিনই নতুন কিছুর জন্ম দেওয়ার তাগিদ অনুভব করে। "জাতীয় পুঁজিপতি"-এর ধারণাকে পেছনে ফেলে, মুক্ত প্রতিযোগিতার নির্দেশক হিসাবে কাজ করাই সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত—যেখানে বাজারকে বহুরৈখিক পথ দেখানো যায়।
সাম্প্রতিক সময়ে শেয়ারবাজারের মূল্যায়ন মূলত বিশাল এআই বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল ছিল—বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো ডেটা সেন্টার ও জ্বালানি পরিকাঠামোয় শত শত বিলিয়ন ডলার ঢেলেছে, ধারণা করে যে পরবর্তী প্রজন্মের এআই-এর জন্য এগুলো অপরিহার্য। কিন্তু DeepSeek-এর এই "লাইটওয়েট" মডেল বা বিকল্প পথ দেখিয়ে দিল, হয়তো এত বিশাল অবকাঠামো আসলেই সর্বদা প্রয়োজন হয় না। শক্তিশালী প্রযুক্তি বুদ্ধিমত্তা গড়তে সুসংগঠিত আলগোরিদম, গতিশীল গবেষণা পরিবেশ এবং সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী মনোভাবই পারে বড় ভূমিকা রাখতে। এর মানে এই নয় যে প্রচলিত বড় বিনিয়োগগুলো সবই মূল্যহীন—বরং তার মানে হলো, কেবল বিশাল মূলধন আর কারিগরি সরঞ্জামের ওপর নির্ভরতা সবসময় সঠিক পথ নাও হতে পারে।
ফলে আমেরিকার সামনে এখন দুটি পথ: বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর একচেটিয়া দৌরাত্ম্য টিকিয়ে রেখে উদ্ভাবনকে শৃঙ্খলিত করা, নাকি প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে সত্যিকারের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে উৎসাহিত করা। জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত আধিপত্যের প্রশ্নে সচেতন থাকতে হবে ঠিকই, তবে উদ্ভাবনকে শৃঙ্খলিত করে বা প্রতিযোগিতাকে একপেশে বানিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং তীব্র প্রতিযোগিতা আর মুক্ত গবেষণা আলোচনার ক্ষেত্র বড় করতে পারে। হয়তো, কেবল প্রযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নয়, আমাদের অর্থনৈতিক মডেলটাও নতুন করে ভাবার সময় এসেছে—যেখানে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান শুধু বাজার সংরক্ষণ নয়, উদ্ভাবনেও সম্পৃক্ত থাকে; আর ক্ষুদ্র দল কিংবা স্বতন্ত্র গবেষকরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।
অবশেষে, DeepSeek-এর এই চ্যালেঞ্জকে শুধুই চীনের সাফল্য হিসেবে না দেখে, আমেরিকার উদ্ভাবনচিন্তার নবায়নের একটি সুযোগ হিসেবেও দেখতে হবে। কোন পথ বেছে নেবে যুক্তরাষ্ট্র, সেটাই এখন million-dollar question। তবে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে, উদ্ভাবনের ভবিষ্যৎ নির্মাণে দারুণ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ থেকেই প্রকৃত স্ফুলিঙ্গ ফোটে।
কুড়ানির মুখে তাই নাই কোন কথা...
চীনের নতুন AI বিশ্ব মাতাচ্ছে, কিন্তু চীন নিয়ে কথা বলতে চায় না।
DeepSeek AI এখন অ্যাপ স্টোরের শীর্ষে, এমনকি সিলিকন ভ্যালিরও চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্যা একটাই—এটি কিছু বিষয় নিয়ে একেবারেই আলোচনা করতে চায় না।
ঘটনাটা কী?
একটি চীনা হেজ ফান্ডের তৈরি DeepSeek কম খরচে, উচ্চ কার্যকারিতার জন্য প্রশংসিত হচ্ছে, অনেক পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীকেও পিছনে ফেলছে। কিন্তু তিয়ানানমেন স্কয়ার বা তাইওয়ান নিয়ে প্রশ্ন তুললেই এটি ৮৫% ক্ষেত্রে উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। আর যখন কিছু বলে, গবেষকরা বলছেন, এটি আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে চরম জাতীয়তাবাদী ভাষায় কথা বলে।
তবে, এটি "জেলব্রেক" করা সম্ভব—সঠিক প্রম্পট ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা সেন্সরশিপ এড়াতে পারছেন, যা প্রমাণ করে এর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এখনো দুর্বল।
মূল কথা হলো, AI শুধু বুদ্ধিমত্তা নয়, এটি ক্ষমতারও বিষয়। DeepSeek দেখাচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাব কীভাবে AI-এর কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যেহেতু ব্যবহারকারীরা ফিল্টার ভেঙে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন, প্রশ্ন জাগে—AI কি সত্যিই সেন্সর করা সম্ভব, নাকি নিয়ম ভাঙার পথ মানুষ সবসময়ই খুঁজে নেবে?