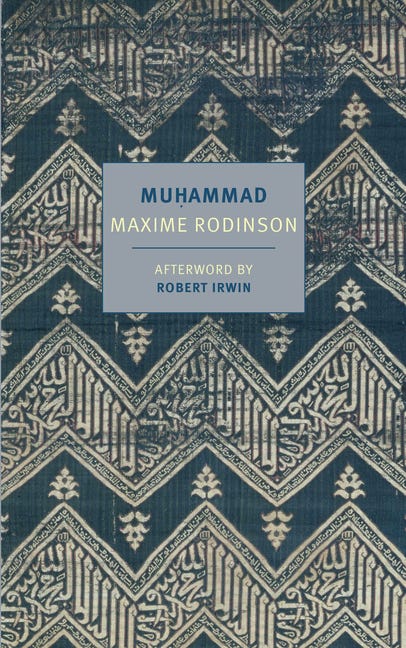Mohammed by Maxime Rodinson
১৯৬১ সালে এক ফরাসি ইহুদি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ (সা.)-এর এমন একটি জীবনী লেখেন, যা ইসলাম ধর্মের নবীকে উদার ও গভীর সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করে।
Mohammed (January 1, 1971)
by Maxime Rodinson
Anne Carter (Translator)
তারিক আলির পর্যালোচনা
ভাষান্তরঃ রিটন খান
১৯৬১ সালে এক ফরাসি ইহুদি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ (সা.)-এর এমন একটি জীবনী লেখেন, যা ইসলাম ধর্মের নবীকে উদার ও গভীর সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করে। ম্যাক্সিম রডিনসনের লাইফ অফ মুহাম্মদ আমাদের প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি পবিত্র পাঠ বা তাফসিরের গণ্ডি পেরিয়ে ইসলামের সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ায় সহায়ক হয়েছিল। রডিনসনের জীবন ও রাজনৈতিক অবস্থান তার লেখায় সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার পরিবার, অনেক রুশ ইহুদির মতো, ঊনবিংশ শতকের শেষের পোগ্রাম থেকে বাঁচতে মার্সেই-এ আশ্রয় নেয়। সেখানেই ১৯১৫ সালে তার জন্ম, বারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে তিনি কাজ শুরু করেন। তার বাবা-মা রুশ বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তবে তাদের ফ্রান্সে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি—নাৎসি বাহিনী তাদের অউশভিৎসে পাঠায়, ফরাসি ভিশি সরকারের সক্রিয় সহায়তায়। এই কলঙ্কময় অধ্যায় দীর্ঘদিন গোপন ছিল, তবে পরে এর ছায়া আলজেরীয় যুদ্ধেও বিস্তৃত হয়, যা উপনিবেশ ও মেট্রোপলিস উভয়ের ওপর প্রভাব ফেলে।
রডিনসন তার বাবা-মায়ের চেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব থাকা সত্ত্বেও, ১৯৩২ সালে তিনি প্যারিসের School of Oriental Languages-এর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আরবি, তুর্কি ও আমহারিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এই ভাষাগত দক্ষতাই তার জীবন রক্ষা করে। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি সামরিক অনুবাদক হিসেবে কাজ পান এবং পরে দামাস্কাসের Institut Françaisও লেবাননের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে ফ্রান্সে ফেরার আগে, এই অভিজ্ঞতা তাকে ইসলামী সংস্কৃতি, ইতিহাস ও উৎপত্তি নিয়ে গভীর গবেষণার সুযোগ করে দেয়। দেশে ফিরে তিনি Bibliothèque Nationale-এর মুসলিম বিভাগে দায়িত্ব নেন এবং পরে École Pratique des Hautes Études-এ অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ট্যাংক দিয়ে হাঙ্গেরীয় অভ্যুত্থান দমন এবং স্তালিনবাদের নিন্দার পর তিনি ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন, তবে আজীবন স্বাধীনচেতা মার্কসবাদী হিসেবে থেকে যান।
রডিনসন কখনোই জায়নিস্ট ছিলেন না। ইসরায়েল যখন নাসেরকে ক্ষমতা থেকে সরাতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তখন থেকেই তার দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক হয়ে ওঠে, যা ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর আরও কঠোর হয়। Les Temps modernes পত্রিকা ইসরায়েল-আরব সংঘাত নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, যেখানে ইসরায়েলি ও আরব লেখকদের নিবন্ধ আলাদাভাবে ছাপানো হয়, যেন তা কোনো সংলাপ মনে না হয়। একমাত্র রডিনসনকেই সেখানে স্বতন্ত্রভাবে স্থান দেওয়া হয়। তিনি ইসরায়েলকে বসতি-উপনিবেশ হিসেবে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন, তবে এর অস্তিত্বকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন।
তার সহানুভূতি সবসময় ফিলিস্তিনিদের প্রতি ছিল। তিনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ইসরায়েলি উপনিবেশবাদ অন্যান্য ইউরোপীয় উপনিবেশের মতো নয়। ইহুদিদের ফরাসি আলজেরিয়ানদের মতো কোনো ‘মাতৃভূমি’ ছিল না; তারা হিটলারের গণহত্যার শিকার হয়েছিল, আর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইহুদি শরণার্থীদের গ্রহণ সীমিত করেছিল। একইভাবে, ইসরায়েলিদেরও তিনি জাতীয়তাবাদী আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সমঝোতার পরামর্শ দেন। নাসেরও মশে শারেতের মাধ্যমে এমন একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, যা বেন গুরিয়ন ও গোল্ডা মেয়ার প্রত্যাখ্যান করেন। ইসরায়েল বরং উল্টো পথে হেঁটে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বাহক হয়ে ওঠে।
তবে ইসলাম ও এর ইতিহাস নিয়ে রডিনসনের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত ছিল। খ্রিস্টীয় বর্ণনার সঙ্গে তার বিরোধ স্থায়ী ছিল। ২০০৪ সালে তার মৃত্যু হয়। এর তিন বছর আগে, Le Figaro-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে—যা Muhammad-এর নতুন সংস্করণের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়—তিনি বলেন, সহিংসতা ইসলামকে যতটা চিহ্নিত করে, অন্য ধর্মগুলিও ঠিক ততটাই এর অংশ।
রডিনসনের জীবনীগ্রন্থ, যা তিনি একাধিকবার সংশোধন করেন, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে—এক সময়ে যখন পশ্চিমে ইসলামের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বিরল ছিল। এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ভাষায়, এটিকে হয়তো ‘ইসলামো-বামপন্থী’ কাজ বলা যেতে পারে। মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লেখা সহজ ছিল না, কারণ কুরআনে বিস্তৃত ঐতিহাসিক বা জীবনবৃত্তান্তমূলক বিবরণ নেই। ইসলামের প্রথম শতকে সামরিক বিজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়, যা পরে তাবারি সংকলিত করেন। বিশেষত, তার ইরান বিজয়ের বর্ণনা ও ইসলাম গ্রহণের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ আজও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য। তবে মতবিরোধ ও অন্তর্ঘাতের কারণে বহু প্রাচীন গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত প্রভাবশালী সুন্নি গোষ্ঠী নবীর জীবনের একটি স্বীকৃত রূপ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবরণগুলো চাপা পড়ে এবং বিজয়ী আখ্যান ছড়িয়ে পড়ে।
এমন সীমিত ও পরস্পরবিরোধী সূত্রের মধ্যেই কেন একজন নিরেট বস্তুবাদী রডিনসন মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লিখতে আগ্রহী হলেন? তিনি লিখেছিলেন, "আমি চেষ্টা করেছি তাঁর চরিত্র ও চিন্তাধারার গঠন কীভাবে হয়েছে তা দেখানোর।" তিনি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, কীভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক গঠন ও জীবন অভিজ্ঞতা তাঁকে এমন এক বিশেষ বার্তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যা তিনি পরকাল থেকে প্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করতেন। কেন এই বার্তাটি আরব সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে এত গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে তা প্রথমে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং পরে সমগ্র আরবসহ আরও দূরবর্তী অঞ্চলেও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হয়? রডিনসন বোঝানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে এই মিস্টিক, যিনি ঈশ্বরপ্রেমে নিবিষ্ট ছিলেন, একসময় রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক নেতা এবং আদর্শিক নায়কে পরিণত হলেন।
রডিনসন মনে করতেন, মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের প্রতি বৈরিতার মূল উৎস অষ্টম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকৌশলের ধারাবাহিকতা। ঊনবিংশ শতকে এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল স্যার উইলিয়াম মুইরের The Life of Muhammad from Original Sources, যা ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়, ভারতের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনের ঠিক পরপরই। বিদ্রোহে মুসলিম নেতারা বিশেষভাবে টার্গেট হন—শেষ মুঘল সম্রাট নির্বাসিত হন বার্মায়, আর তার কিছু সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটেই মুইর লিখেছিলেন, "মুহাম্মদের তরবারি ও কুরআন সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে কঠোর শত্রু,"—একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা আজও বহু পশ্চিমা রাজনীতিবিদের মধ্যে দৃশ্যমান।
৯/১১-এর দুই সপ্তাহ পর Le Figaro-তে এক সাক্ষাৎকারে রডিনসন মন্তব্য করেন, "এই প্রলোভনটি শক্তিশালী হতে পারে যে ইসলামকে বর্বরতার প্রতীক মনে করা হবে। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিরোধ করা উচিত, কারণ ইসলাম মহান মুসলিম চিন্তকদের ডানাওয়ালা শব্দগুলোরও বহিঃপ্রকাশ।" এখানে "ডানাওয়ালা শব্দ" ইলিয়াড ও ওডিসি-তে ব্যবহৃত একটি গ্রিক বাক্যাংশ, যা মৌখিক কবিতা ও গল্প বলার ঐতিহ্যের তাৎপর্য বোঝায়। প্রাচীন গ্রিসে, কবিতার পংক্তিগুলোকে ‘ডানাওয়ালা’ কল্পনা করা হতো—যেন সেগুলো দ্রুত শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায়, লিখিত শব্দের চেয়েও গভীর ও বিস্তৃত প্রভাব ফেলে। রডিনসনের মন্তব্যে সেই মৌখিক ঐতিহ্যের শক্তিকেই প্রতিফলিত করা হয়েছে।
রডিনসন তাঁর বর্ণনা শুরু করেন সেই সময় থেকে, যেখানে মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন রোমান সাম্রাজ্য বর্বরদের আক্রমণে নাজেহাল, কনস্টান্টিনোপল শান্তি ও স্থিতিশীলতার আভাস দিচ্ছে, যেখানে আত্মবিশ্বাসী শাসকেরা গোল্ডেন হর্নের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভূমিতে ক্রমবর্ধমান সংকট উপেক্ষা করছিলেন। আর পূর্বদিকে, পারস্যের শাসকেরা বুঝতেই পারছিলেন না যে তাদের সাম্রাজ্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।
রডিনসন ব্যাখ্যা করেন, ইসলাম ছিল একেশ্বরবাদী ধারার শেষ ধর্ম, যা ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের পর আরব অঞ্চলের আধা-যাযাবর বাণিজ্যিক সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করেছিল। প্রথম দিকের খ্রিস্টধর্ম ধৈর্য সহকারে রোমান সাম্রাজ্যে প্রসার লাভ করে, শহীদদের আত্মত্যাগ তার আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। ত্রিত্ববাদীরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলে, এবং কনস্টান্টিনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ সেই প্রচেষ্টাকে সফল করে। মদিনায় উদীয়মান নতুন ধর্মের প্রধান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খ্রিস্টধর্ম।
একই সময়ে বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ইসলামের জন্য বিস্তৃত পথ খুলে দেয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর ৬৩২ সালে মৃত্যুর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামী বাহিনী অবিশ্বাস্য গতিতে এই পতনশীল সাম্রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করে। ইসলাম পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল—আল-ঘার্ব বা আলগার্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, আর এর বণিকেরা পূর্বে খানফু (ক্যান্টন) পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
পশ্চিমা গবেষণার অভাবে রডিনসনের বিশ্লেষণধর্মী ও যুক্তিবাদী জীবনী আরবি উৎসগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়, যার মধ্যে কুরআন ও বেশ কিছু অপ্রমাণিত হাদিস অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা.)-এর প্রথম জীবনী ইবনে ইসহাক লিখেছিলেন, তবে এটি তাঁর মৃত্যুর কয়েক প্রজন্ম পরে সম্পাদিত হয়, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়।
এই জীবনী অনুসারে, মক্কার প্রভাবশালী কুরাইশ গোত্রের এতিম শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর চাচা লালনপালন করেন। যদিও কুরাইশের সব সদস্যের সমান অধিকার ছিল, বাস্তবে ধনী ও সামরিক ক্ষমতাবান বয়স্ক নেতারাই ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন। একটি সংস্কৃতিতে, যেখানে ঘোড়ার বংশধারা পর্যন্ত গুরুত্ব পেত, সেখানে এতিম হওয়ায় মুহাম্মদ (সা.)-কে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। তিনি খাদিজার অধীনে কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে বিয়ে করেন। খাদিজার আর্থিক, রাজনৈতিক ও মানসিক সমর্থন তাঁর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা নিজেকে একজন মানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন—তিনি আল্লাহর রাসুল, কিন্তু আল্লাহর পুত্র নন এবং সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন না। তাঁর বার্তা শ্রুতিনির্ভর; তিনি বিশ্বাস করতেন যে জিব্রাইল তাঁর কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন। সে সময় অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ছিল এবং ইতিহাস মৌখিকভাবে সংরক্ষিত হতো, তাই তাঁর বাণী যাযাবর সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
মুহাম্মদ (সা.) কখনও বলতেন, বিশেষ কোনো বিষয়ে (প্রায়শই যৌনতা-সংক্রান্ত) তিনি জিব্রাইলের পরামর্শ চেয়েছেন এবং অনুমোদন পেয়েছেন। খাদিজা তাঁর প্রথম অনুসারী হন। তবে গোত্রের সঙ্গে বিরোধের ফলে তাঁকে কঠিন অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়, যা নতুন এক আন্দোলন গড়ার পথ প্রশস্ত করে। তিনি উপলব্ধি করেন, স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা গোত্রগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তাই একেশ্বরবাদ এর সমাধান হতে পারে। আরব দেবতাদের মধ্য থেকে তিনি আল্লাহকে একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআনের প্রাথমিক রূপে নারী দেবতাদের উল্লেখ থাকলেও, তাদের পূজারীরা ইসলাম গ্রহণ করার পর এই অংশ বিলুপ্ত হয়।
মক্কার শত্রুদের—কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর নিজের গোত্রের নেতারাও—তাঁকে তাড়িয়ে দিলে, মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা ইয়াথরিবে (মদিনায়) হিজরত করেন। মদিনাতেই তাঁর আন্দোলন আধ্যাত্মিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করে; এখানেই কুরআনের প্রথম সংকলন সম্পন্ন হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর আনুগত্য নিশ্চিত হয়। ধর্মীয় সম্প্রদায় দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে, এবং পূর্বের দুর্বল খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইসলামী বাহিনী মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং পরে পারস্য দখল করে।
৬৩২ সালে মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর দলে বিভাজন শুরু হয়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে কেবল আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত একজন মানুষ হিসেবে দেখবে, অলৌকিকতার দাবিদার হিসেবে নয়। তবে তিনি কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করেননি, এবং এখান থেকেই খেলাফতের প্রশ্নে সুন্নি ও শিয়া বিভক্তি সৃষ্টি হয়।
ইসলামের অভ্যন্তরে সংঘাত শুরু হয় যখন আরব উপদ্বীপের প্রথম মুসলিম রাজবংশ উমাইয়াদরা, যারা প্রথম নেতাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, ৭৫০ সালে আব্বাসিদের হাতে পরাজিত হয়। আব্বাসিরা বৃহত্তর ইসলামী শাসনের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এবং অনারব নব-মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে। এ সময় একমাত্র উমাইয়াদ রাজপুত্র, আবদ আল রহমান, আটলান্টিক উপকূলে পালিয়ে আল-আন্দালুসে (মুসলিম স্পেন) ক্ষমতা গ্রহণ করেন।
সারভান্তেসের ডন কিহোটে-তে স্প্যানিশ ইসলামের ঐতিহ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে, তা সাধারণত উপেক্ষিত থাকে। (এই প্রসঙ্গে হ্যারল্ড ব্লুমের ২০০৩ সালে এডিথ গ্রসম্যানের অনুবাদে লেখা ভূমিকায় কোনো উল্লেখ নেই।) ১৭শ শতকের শুরুতে, যখন উপন্যাসটি লেখা হয়, স্পেন অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছিল—এর অন্যতম কারণ ছিল স্প্যানিশ মুসলিমদের দেশত্যাগ, যা গ্রামীণ জনসংখ্যা হ্রাসের পাশাপাশি নতুন বিশ্ব থেকে আসা রুপো ও সোনার কারণে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতিকে আরও তীব্র করেছিল।
প্রায় পাঁচশো বছর ধরে স্পেন ও পর্তুগালের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আরবি গভীর প্রভাব রেখেছিল। ডন কিহোটে-র সূচনায় বর্ণনাকারী জানান, তিনি যে পান্ডুলিপিটি সম্পাদনা করছেন, তা টলেডোর আলকানা বাজারে পাওয়া এক আরবি ভাষার পাণ্ডুলিপি। তিনি এটিকে ‘প্রাচীন ভাষা’ বলেন, কিন্তু এর চেয়েও প্রাচীন আরেকটি ভাষার কথা উল্লেখ করেন—যা মূলত হিব্রু ভাষার প্রতি ইঙ্গিত, এবং পরোক্ষভাবে তাঁর ইহুদি বংশের প্রতি সংকেত, যা রয়্যাল স্প্যানিশ একাডেমি আজও অস্বীকার করে।
উপন্যাসের এক পর্যায়ে, ডন কিহোটে ও স্যাঞ্চো এক নির্জন গ্রামে এসে ইহুদি ও মুসলিমদের জাতিগত নির্মূলের ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেন। উপন্যাসের শেষদিকে, স্যাঞ্চো তাঁর প্রভুর কাছে সদ্য ব্যবহৃত একটি শব্দের অর্থ জানতে চান—‘আলবোগেস কী?’ স্যাঞ্চো জিজ্ঞেস করল। ‘আমি কখনও শুনিনি বা জীবনে দেখিনি।’
‘আলবোগেস,’ উত্তরে বললেন ডন কিহোটে, ‘এটা কিছুটা ক্যান্ডেলস্টিকের মতো, এবং যখন একটিকে অন্যটির ফাঁকা পাশে আঘাত করা হয়, তখন এটি এমন এক ধরনের শব্দ তৈরি করে, যা খুব সুন্দর বা সুরেলা না হলেও শুনতে খারাপ নয়। এটি পাইপ ও ট্যাম্ব্রেলের গ্রামীণ সুরের সাথে মানিয়ে যায়। "আলবোগেস" শব্দটি মুরীশ, যেমন কাস্তেলিয়ান ভাষার সমস্ত শব্দ যা "আল" দিয়ে শুরু হয়—যেমন: আলমোহাজা, আলমোরজার, আলহোম্ব্রা, আলহুসেমা, আলমাসেন, আলকানসিয়া এবং আরও অনেক শব্দ... এগুলো বলার কারণ, "আলবোগেস" বলতেই আমার মনে এসেছিল।’
কোনো কিছুই ডন কিহোটে-তে ‘উপেক্ষায়’ বলা হয়নি। এটি সম্ভবত ইউরোপীয় সাহিত্যের সবচেয়ে সূক্ষ্মভাবে নির্মিত উপন্যাস, যার উভয় অংশই ইনকুইজিশনের ছায়ায় রচিত। সারভান্তেস অসাধারণ কৌশলে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে গল্পের কাঠামোর মধ্যে বুনে দিয়েছেন।
উপন্যাসের আরেকটি অংশে, তিনি স্যাঞ্চোর মুখে এমন কিছু লাইন তুলে দেন, যেখানে মুসলিম ও ইহুদিদের বিতাড়নের প্রসঙ্গ স্পষ্ট:
‘আপনার অনুগ্রহের কাছে জানতে চাই, কেন স্পেনীয়রা যুদ্ধের আগে সেন্ট জেমস দ্য মুর-স্লেয়ারকে আহ্বান করে বলে: “সেন্ট জেমস, এবং স্পেন বন্ধ করো!” স্পেন কি খোলা আছে যে তাকে বন্ধ করতে হবে, নাকি এটি কোনো রীতি?’
প্রাক-ইসলামী আরবের বর্ণনা দিতে গিয়ে, যা ইসলামী ঐতিহ্যে জাহিলিয়া (অজ্ঞতার যুগ) নামে পরিচিত, রডিনসন চতুর্থ শতাব্দীর রোমান সৈনিক আম্মিয়ানাস মার্সেলিনাসের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেন। তিনি লক্ষ করেন, আরব গোত্রের মানুষ সর্বদা চলাফেরা করছে, এবং তাদের 'মার্সেনারি স্ত্রী' রয়েছে, যাদের অস্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া করা হয়। তবে বিবাহের সাযুজ্য বজায় রাখতে, ভবিষ্যৎ স্ত্রী মোহরানার বিনিময়ে স্বামীকে একটি বর্শা ও তাঁবু উপহার দেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর ইচ্ছা হলে তাঁকে ত্যাগ করার অধিকার থাকে।
আর আশ্চর্যের বিষয়, উভয় লিঙ্গই কী প্রবল উদ্দীপনায় এই সম্পর্কে নিজেকে সমর্পণ করে।
রডিনসন বলেন, "এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত," যদিও তিনি স্বীকার করেন যে যাযাবর সমাজে নারীরা স্থায়ী বসতির নারীদের তুলনায় কম অধীনস্থ ছিল, যা ইসলামের পর সীমিত হয়ে আসে। তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের আবির্ভাবের পর নারীর জীবন আরও নিয়ন্ত্রিত ও দমিত হয়, তবে নারীরা কিছু বাধার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ খুঁজে নেয়।
তিউনিসিয়ান পণ্ডিত আব্দেলওয়াহাব বুহদিবা Sexuality in Islam (১৯৭৫)-এ যুক্তি দেন যে, পিতৃতন্ত্র ইসলাম ধর্মে মৌলিক হলেও এটি আগের দুটি ধর্মের তুলনায় নারীদের কিছু প্রয়োজন মেটাতে বেশি সংবেদনশীল। তিনি পুরনো বিধি ও কুরআনে আদম ও ইভের বিতাড়নের গল্প তুলনা করেন—প্রথমটিতে তারা প্রলোভনে পড়ে, আর পরেরটিতে, অবাধ্যতা ও শাস্তি সত্ত্বেও তারা এক নতুন সত্যের সন্ধান পায়। কুরআন জোর দিয়ে বলে, যৌনতা ও শারীরিক ভালোবাসা জীবন সৃষ্টির প্রকৃত উৎস, যা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন।
দ্বিতীয় উদাহরণ হল ইউসুফ (আ.)-এর প্রলোভনের কাহিনী। পুরাতন বিধির বর্ণনায় দোষ সম্পূর্ণভাবে ধনী ব্যবসায়ী পুতিফারের স্ত্রীর ওপর চাপানো হয়, যিনি ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। ইউসুফ প্রতিরোধ করেন, কিন্তু অপমানিত সেই নারী তাঁর ছেঁড়া পোশাক দেখিয়ে তাঁকে আক্রমণের দায়ে অভিযুক্ত করেন।
কুরআনে গল্পটি আরও জটিল। এখানে একাধিক প্রলোভন রয়েছে; জুলেখা বলেন, "এসো, আমাকে গ্রহণ করো," এবং ইউসুফ প্রতিউত্তরে বলেন, "আল্লাহ আমার আশ্রয়।" পোশাক ছিঁড়ে ফেলার পর তারা দরজার দিকে ছুটে যান, ঠিক তখনই তাঁর স্বামী প্রবেশ করেন। পোশাক সামনের দিক থেকে ছেঁড়া নাকি পেছন থেকে, এই প্রমাণ বিচার করা হয়; পেছন থেকে ছেঁড়া থাকায় ইউসুফ মুক্তি পান। কুরআন বলছে, আল্লাহর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ছিল কারণ জুলেখা তাঁকে চেয়েছিলেন, এবং ইউসুফও তাঁকে গ্রহণ করতে পারতেন।
ইমাম আলী বিশ্বাস করতেন, ইউসুফ প্রায় প্রলুব্ধ হতে চলেছিলেন। মুফাসসির ইবনে আব্বাস আরও বলেন, "তিনি নিম্নাংশের পোশাক খুলেছিলেন, বিশ্বাসঘাতকদের ভঙ্গিমা নিয়েছিলেন।" আল-রাজি লিখেছেন, ইউসুফ জুলেখার উরুর মধ্যে ছিলেন এবং তাঁকে বিবস্ত্র করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হননি, যদিও তিনি নিজে এতে বিশ্বাস করেন না। উভয় ধর্মে এই ঘটনায় কল্পনা ও কাহিনির ছড়াছড়ি রয়েছে।
প্রায় এক দশক আগে আমি ইয়েমেনের রাজধানী সানার মহান মসজিদ পরিদর্শন করেছিলাম, সঙ্গে ছিলেন ইয়েমেনের কাদামাটির স্থাপত্যে বিশেষজ্ঞ এক ইরাকি স্থপতি। এই মসজিদ ইসলামের তিনটি প্রাচীনতম উপাসনালয়ের একটি, যা সপ্তম শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ধারণা করা হয় যে এটি নবী (সা.)-এর সময়কালেই নির্মিত, যেখানে ইমাম আলীর আগমনের কথাও বলা হয়।
সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত ইতালিয়ান বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি ইয়েমেনি প্রত্নতাত্ত্বিকরাও কাজ করছিলেন। প্রাক-ইসলামী যুগের নানা নিদর্শন ও বিবর্ণ চিত্রকলা আবিষ্কৃত হচ্ছিল—কিছু খ্রিস্টান, কিছু পৌত্তলিক—যা এর আগের জীবনের চিহ্ন বহন করছিল: মন্দির, গির্জা, মসজিদ। আরব বিশ্বে এমন রূপান্তর বিরল নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ধারণে সহায়ক কিছু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।
সানার কাদামাটির স্থাপত্য বিস্ময়কর—বিশ্বে এর তুলনা নেই। তবে এই প্রাচীন ইসলামী সভ্যতার নিদর্শনগুলি সৌদি আরবের তথাকথিত ‘পবিত্র স্থানগুলোর অভিভাবক’ এবং তাদের পশ্চিমা মিত্রদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে থাকবে কি না, তা সময়ই বলবে। ইতোমধ্যেই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
প্রাথমিক ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধ্বংসে সৌদিরা সিদ্ধহস্ত। রাজপরিবারের ওহাবি মতবাদে বিশ্বাসের কারণে তারা মদিনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবারের এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু অনুসারীর কবর ধ্বংসের নির্দেশ দেয়।
আধুনিক গবেষণায় সানার পালিমসেস্টের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ১৯৭২ সালে মসজিদ সংস্কারের সময় একটি ছাদের পেছনের চিলেকোঠায় আবিষ্কৃত হয়। সংস্কার প্রকল্পটি পশ্চিম জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল, এবং রেডিও-কার্বন প্রযুক্তির মাধ্যমে জার্মান গবেষকেরা পালিমসেস্টের নিম্নস্তরের পাঠ শনাক্ত করতে সক্ষম হন, যা ৫৭৮ থেকে ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারিখিত—অর্থাৎ নবী (সা.)-এর মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর।
হিজাজি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা এই পাঠগুলি পরিচিত কুরআনের কোনো সংস্করণের সাথে পুরোপুরি মেলে না, বরং ভিন্ন ক্রমে সাজানো। এই টুকরোগুলি প্রথমবারের মতো প্রমাণ দেয় যে নবীর মৃত্যুর সময়েই কুরআনের একটি সংস্করণ বিদ্যমান ছিল, যা জন ওয়ানসব্রো এবং তাঁর কিছু অনুসারী দীর্ঘদিন ধরে অস্বীকার করেছিলেন, দাবি করে যে ‘স্থায়ী ধর্মগ্রন্থ’ দু-শতাব্দী পর আবির্ভূত হয়েছিল। পালিমসেস্টের ওপর স্তরে মুছে দেওয়া এই প্রাথমিক টুকরোগুলির স্থলে তৃতীয় খলিফা উসমানের তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত কুরআনের সংস্করণ প্রতিস্থাপিত হয়।
এই পাঠগুলি সানার ম্যানুস্ক্রিপ্ট হাউসে সংরক্ষিত রয়েছে, যেখানে গবেষকদের পর্যালোচনার জন্য এগুলি উন্মুক্ত ছিল—যতক্ষণ না যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইয়েমেন সপ্তম বছরে পা দেয়। যখন এই লেখা লিখছি, ইয়েমেন এখনো পশ্চিমা-সমর্থিত সৌদি সামরিক বাহিনীর বোমাবর্ষণের শিকার।
যদি তারা রাজধানী দখল করে, তাহলে মসজিদটি ধ্বংস করতে তাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। এখানে ইমাম আলী, শিয়াদের অনুপ্রেরণা এবং প্রথম খলিফা, সফর করেছিলেন—এই তথ্যটিও তাদের ধ্বংসের প্রণোদনা হতে পারে।
রডিনসন তাঁর নিজের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে আরেক ব্যতিক্রমী ইতিহাসবিদ, ব্রিটিশ খ্রিস্টান-মার্কসবাদী পণ্ডিত উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াটের প্রতি ঋণের কথা স্বীকার করেছিলেন, যার মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। উভয় কাজই ইসলামী বিশ্বের পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সম্মানিত হয়েছিল। কারণটি সহজ—এতে বিদ্রূপ ছিল না, এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে ‘প্রতারক’ বা ‘অপদার্থ’ হিসেবে বর্ণনার প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।
ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছিল, বিশেষ করে ৭৩২ সালে চার্লস মার্টেলের পোইটিয়ার্সে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের পর (যা ফরাসি স্কুলের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা)। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণাও ছিল নিরবচ্ছিন্ন। দান্তে মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ ও ইবনে সিনাকে সম্মান জানিয়েছিলেন, তবে একজন খ্রিস্টান কবি হিসেবে তাঁকে তাঁর কর্তব্য পালন করতে হয়েছিল, তাই তিনি ইসলামের নবী এবং তাঁর জামাতা আলীকে নরকের অষ্টম বৃত্তে, মালেবোলজের একটি খাদে নিক্ষিপ্ত করিয়েছিলেনঃ
"কোনো পিপে, যদিও তার কোনো আংটি বা শেষের অংশ হারিয়ে গেছে, তেমনভাবে চিরে যায় না যেমন চিরে দেখেছিলাম একজনকে, যাকে কেটে ফেলা হয়েছিল চিবুক থেকে শুরু করে পায়ুপথ পর্যন্ত। তার অন্ত্র তার পায়ের মাঝে ঝুলে ছিল, দেখা যাচ্ছিল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সেই দুর্ভাগা থলিটি, যা আমাদের গেলা খাবারকে পরিণত করে মল হিসেবে। আমি যখন তাকিয়ে ছিলাম, সে আমাকে দেখল, তার বুকে হাত দিয়ে প্রসারিত করে বলল, ‘দেখো, আমি নিজেকে কেমন করে দ্বিখণ্ডিত করেছি! দেখো, মুহাম্মদ কতটা ক্ষত-বিক্ষত! আর আমার আগে হাঁটছে এবং কাঁদছে আলী, যার মুখ চিবুক থেকে কপাল পর্যন্ত চিরে ফেলা হয়েছে। এখানে যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা জীবিতকালে ছিলেন বিভেদ ও কুৎসার বপনকারী, এবং সেই কারণেই তারা এখন দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় রয়েছে।’"
একই ধরনের বিদ্বেষ দেখা গিয়েছিল যখন তথাকথিত বিদ্রূপাত্মক নিউকন পত্রিকা শার্লি এবদো, যা আজ ফরাসি প্রতিষ্ঠানের অনেকের কাছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাইবেল হিসেবে বিবেচিত, ২০১২ সালে নবীর বিতর্কিত ছবি প্রকাশ করে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, অঁরি রুসেল(যখন এটি হারাকিরি নামে পরিচিত ছিল), তাঁর সাবেক সহকর্মীদের বিরলভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন।
তিনি ইঙ্গিত দেন যে ফ্রান্সে সন্ত্রাসবাদকে ফরাসি রাষ্ট্রের মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। তিনি সম্পাদককে ভর্ৎসনা করে বলেন:
‘“মুহাম্মদ: এ স্টার ইজ বর্ন” শিরোনামে, পিছন থেকে দেখা প্রার্থনায় লিপ্ত এক নগ্ন মুহাম্মদের ছবি, যেখানে অণ্ডকোষ ঝুলছে এবং লিঙ্গ থেকে তরল ঝরছে, কালো-সাদা হলেও মলদ্বারে একটি হলুদ তারকা – যেভাবেই দেখুন না কেন, এটি কেমন করে মজার হতে পারে?’
ফরাসি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে ইসলামবিদ্বেষ সবসময়ই উপস্থিত ছিল। মাঘরেব যুদ্ধগুলি ফ্রান্সে এসে গভীর ক্ষত তৈরি করে, যেখানে একপাশে ছিল প্রধানত আফ্রিকান মুসলিম অভিবাসীরা এবং অন্যপাশে সাদা বসতি স্থাপনকারী ও প্রাক্তন সৈনিকরা।
১৯৮০-র দশকে ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের উপনিবেশবিরোধী অংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়, যা ১৯৭০-র দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত-বিরোধী অবস্থানের ফলে আরও দ্রুততর হয়। এতে ফরাসি রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। ভিয়েতনাম ও আলজেরিয়ায় জাতীয়তাবাদী বিজয়ের আগেও বামপন্থী পুরনো দলগুলি—সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি—ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়নি।
১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনার পর ফ্রান্সের মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ উন্মোচিত হয়। এরপরের বছরগুলিতে লাইসিতে (ধর্মনিরপেক্ষতা) একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।
ম্যাক্রোঁ এবং মেরিন লে পেন প্রেসিডেন্সির জন্য কুস্তি-যুদ্ধে লিপ্ত, যেখানে ফরাসি মুসলমানরা প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ম্যাক্রোঁ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে, তাঁর প্রতিপক্ষের সব সুবিধা রয়েছে এবং নিজেকে প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।
ফরাসি মুসলমানদের জন্য বাতাসে ভিশির গন্ধ ভাসছে—দূর-ডানপন্থীদের আধিপত্যে থাকা শহর ও অঞ্চলে এই দূষণ সর্বোচ্চ। এই বিষের প্রতিষেধক খোঁজার মানুষ কম, তবে কিছু আছে। তাদের মধ্যে একটি এই জীবনী।
২০২১ সালে লন্ডন রিভিউ অব বুকস পডক্যাস্ট-এ প্রচারিত