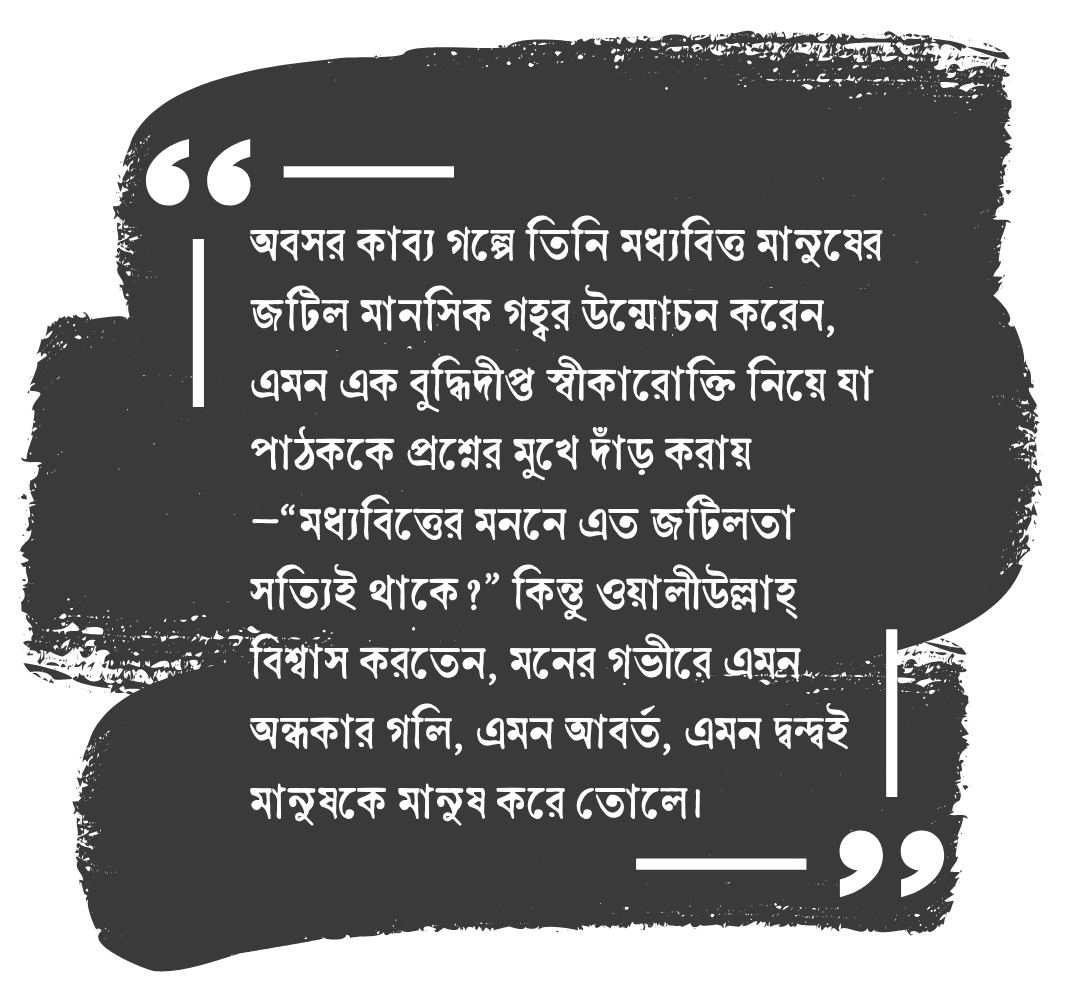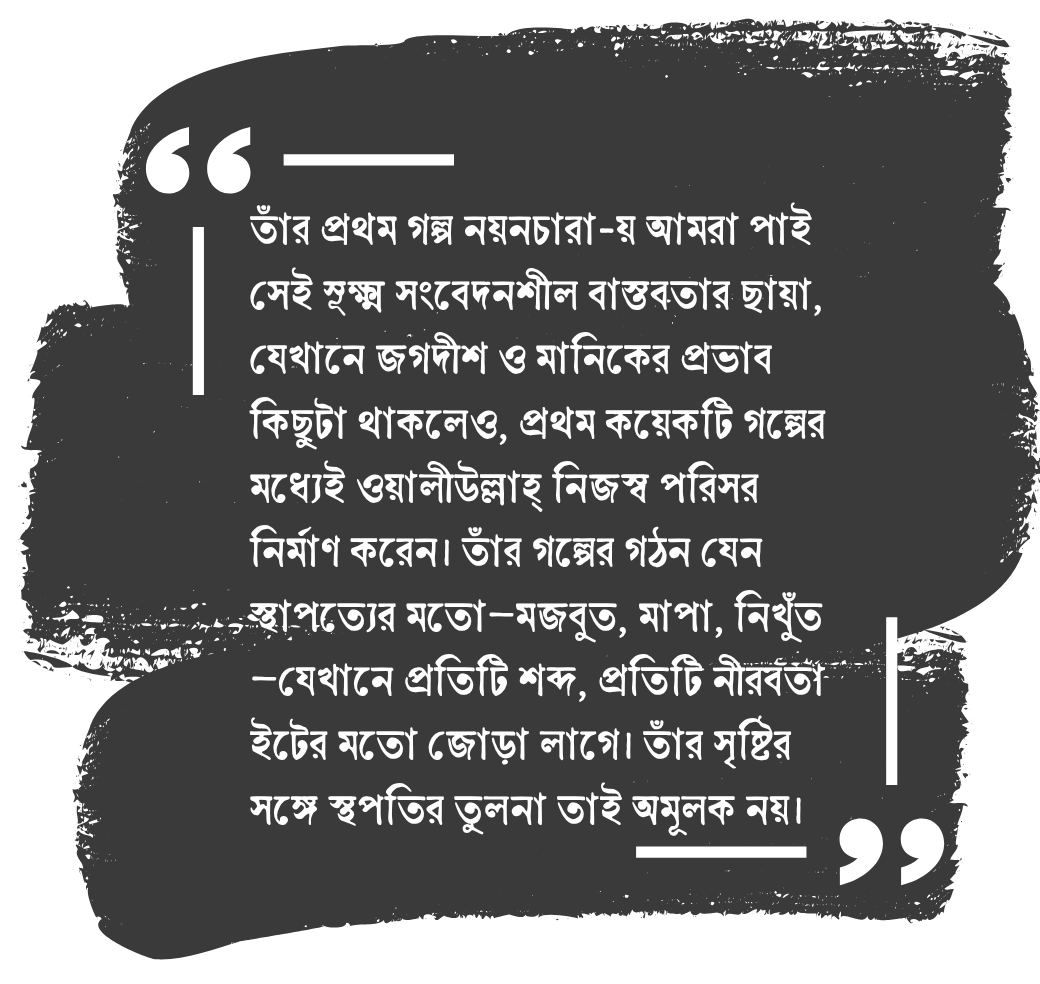সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: বাংলা ছোটগল্পের নির্মাণভূমিতে এক নিঃশব্দ স্থপতি
এই নিবিড় মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, এই নিরীক্ষাধর্মী নির্মাণশৈলীই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্থায়ী এবং একক করে তুলেছে—যেখানে গল্প হয়ে ওঠে মননের প্রতিচ্ছবি, আর প্রতিটি শব্দ এক এক
রিটন খান
আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে BDNews24. ক্লিক করে সেখানেও পড়তে পারেন অথবা এখানেও।
বাংলা ছোটগল্প এক আশ্চর্য রত্নভান্ডার—যার দরজা প্রথম উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে খুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই আবিষ্কারের পর থেকে যেন এক অবিরাম অনুসন্ধানযাত্রা শুরু হয়েছে, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সুর, চরিত্র, শৈলী আর চিন্তার ভুবনে বাংলা গল্পের ভূমি প্রসারিত হয়েছে। এই রত্নখচিত সাহিত্যের অঙ্গন গড়ে উঠেছে বহু প্রজন্মের গল্পকারদের নিবিড় সাধনা, ক্লান্তিহীন অনুশীলন, এবং সৃষ্টিশীল দায়বদ্ধতার ভিতের ওপর। তাই কোনও এক লেখকের গল্প নিয়ে কথা বলতে গেলেই অবধারিতভাবে এসে পড়ে সমগ্র বাংলা গল্পধারার প্রসঙ্গ—কারণ এই ধারা একক নয়, এটি নদীর মতো—অবিরাম, সজীব, বহমান।
এই নদীর স্রোতপথে প্রতিটি স্রষ্টা নিজের ঢেউ তুলেছেন, ভাষা ও নির্মাণশৈলীর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোথাও বাঁক নিয়েছেন, কোথাও ভেঙেছেন প্রচলিত গতি, কিন্তু প্রবাহের প্রাণশক্তি কখনও থেমে যায়নি। গল্প শুধু পরিমাণে বা পরিসরে নয়, তার বৈচিত্র্য ও গভীরতায়ও এক অন্তহীন বিস্তার। একেকজন লেখক এই চলমান ধারার মধ্যে নিজেদের স্বকীয়তায় অনন্য হয়ে উঠেছেন—যেমন তাঁদের কেউ ভাষাশিল্পী, কেউ গঠনকারিগর, কেউ বা নিঃশব্দে জীবন ও মাটির কথক।
সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও নির্মাণশৈলী যখন গঠনের সঙ্গে একীভূত হয়, তখন গল্প কেবল বলা নয়, হয়ে ওঠে এক স্থাপত্যকর্ম। সেখানে “কি গাঁথলেন” যেমন দেখার বিষয়, “কেমন করে গাঁথছেন” তাও সমান আকর্ষণীয়—যার ভিতরেই লুকিয়ে থাকে সৃষ্টির নৈঃশব্দ্যময় সৌন্দর্য। এই অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা ছোটগল্পের সেই স্থপতি, যার রচনায় দেখা মেলে পরিপূর্ণ স্থাপত্যের মাধুর্য এবং নির্মাণের সূক্ষ্ম কৌশল। তাঁর গল্প পড়তে হয় মনোযোগ দিয়ে, ধীরে ধীরে, যেন এক একটি ইট বসানো হচ্ছে নির্মিতির সময়।
ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পকে পুনরায় বলা যায় না, সংক্ষিপ্ত করা যায় না, কারণ গল্পের প্রাণ লুকিয়ে আছে প্রতিটি শব্দের ব্যবহারে, প্রতিটি বিরতির ভেতর। তার মর্মার্থকে আলাদা করে নেওয়া মানেই নির্মাণের প্রাণ কেড়ে নেওয়া। তাই তাঁর গল্প পাঠ মানে এক সম্পূর্ণ ও সচেতন অভিজ্ঞতা—যেখানে পাঠকও একপ্রকার নির্মাতা হয়ে ওঠে, গল্পের স্থাপত্যে নিজের উপস্থিতি রেখে যায়। এইভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা ছোটগল্পের ভাষা ও গঠনকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছিলেন।
মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবন—১৯২২ থেকে ১৯৭১। কিন্তু এই স্বল্প জীবনের ভেতরেই প্রায় তিন দশকব্যাপী এক নিরলস সাহিত্যসাধনা। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট—এই তিন দশক যেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কলমের ধারার তিন অধ্যায়। শুরুটা ছোটগল্প দিয়ে—যেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে জীবনের বৃহৎ সত্যকে ধরার এক তীব্র আকুলতা। পরে ধীরে ধীরে তাঁর মনোযোগ গিয়ে পড়ে উপন্যাসে, নাটকে। গল্প তাঁর সৃষ্টিজীবনের প্রথম দেড় দশকের ধ্রুবতারা, যেখান থেকে তিনি তাঁর পরবর্তী সাহিত্যের আলোকরেখা খুঁজে পেয়েছিলেন।
শেষ পর্যন্ত তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা ৫৩—এ যেন এক জীবনের পরম হিসাব। প্রথম গল্পগ্রন্থ নয়নচারা প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে (সম্ভবত ১৯৪৪ সালেও হতে পারে) পূর্বাশা প্রকাশনী থেকে। সেইখানেই তাঁর গল্পকার সত্তার আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয় এবং শেষ গল্পগ্রন্থ দুই তীর ও অন্যান্য গল্প বেরোয় প্রায় বিশ বছর পর, ১৯৬৫ সালে। দুটি গ্রন্থ মিলিয়ে গল্পের সংখ্যা মাত্র সতেরো—কিন্তু বাকিগুলো বহু বছর অগ্রন্থিত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিল পত্রপত্রিকায়। পরে ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রন্থাবলী, যেখানে আগের সতেরোর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও বত্রিশটি গল্প। পরবর্তীতে আরও চারটি গল্পের সন্ধান মেলে, যা মিলিয়ে তাঁর গল্পসংখ্যা দাঁড়ায় তিপ্পান্ন—এক পূর্ণাঙ্গ, আপাতচূড়ান্ত সংগ্রহ।
ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম গল্প নয়নচারা প্রকাশিত হয় পূর্বাশা পত্রিকায়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘন ছায়া, তার সঙ্গে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো ছায়া—বাংলার আকাশে মাটি জুড়ে মৃত্যু, অনাহার, শূন্যতা। এই প্রেক্ষাপটে তরুণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখছেন নয়নচারা, মৃত্যু-যাত্রা, রক্ত—গল্প, যেগুলির ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিজের অন্তর্গত রক্তক্ষরণ, মানুষের অবিরাম ক্ষুধা ও হাহাকারের মর্ম।
যুদ্ধ আর মন্বন্তর শুধু খিদে বাড়ায়নি, মুছে দিয়েছিল মানুষের আবেগের মাটি, কৈশোরের কোমলতা, স্নেহের নরম আশ্রয়। ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন, কীভাবে ক্ষুধা মানুষের বুকের ভেতরকার ‘জমিন’ কেড়ে নিয়ে তাকে করে তোলে ছিবড়ে, হাভাতে ভিখিরি। কিন্তু তাঁর গল্পে খিদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় অন্য এক খিদে—হারানো মাটির খিদে, হারানো মায়ের খিদে। নয়নচারা-র প্রথম পংক্তিই যেন এই অন্তর্গত তৃষ্ণার প্রতীক—“ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ুরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে।”
এখানে ক্ষুধা কেবল শারীরিক নয়; এটি স্মৃতির, মাতৃভূমির, মমতার অভাবের এক অতল তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার তীব্রতা ধরা পড়ে তাঁর বর্ণনায়—“সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল আপাদমস্তক।” অবশেষে যখন “কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্ত গলায় শুধু বলল: নাও,” তখন সেই একবেলা ভাত হয়ে ওঠে জীবনের প্রতীক।
ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে যে মানুষ ভাত নিচ্ছে, তার মুখ তুলে চাওয়ায় ফুটে ওঠে যেন মাতৃস্মৃতির স্নেহছায়া। মেয়েটির মুখে সে খুঁজে পায় সেই চিরচেনা মুখ—নয়নচারা গ্রামের উঠোনে, যেখানে মা ভাত বেড়ে দেয়। রান্নাঘরের ধোঁয়া, পিড়ির পাশে সাজানো থালা—সব যেন হঠাৎ ফিরে আসে স্মৃতির আলোকছায়ায়। আর তখনই মাটি-সন্ধানী সেই সন্তানের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অশ্রুসিক্ত প্রশ্ন, “নয়নচারা গায়ে কী মায়ের বাড়ি?”
এই একটি প্রশ্নেই যেন ওয়ালীউল্লাহ্র সমগ্র সাহিত্যজীবনের উত্তর নিহিত—মানুষের চিরন্তন অন্বেষা, যেখানে ক্ষুধা মিশে যায় মায়ায়, মৃত্যু মিশে যায় জীবনের সন্ধানে। তাই তাঁর গল্প কেবল গল্প নয়—তা এক মাটিলগ্ন আত্ম-উপলব্ধির আখ্যান, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজের মায়ের বাড়ির পথ দেখায়।
খিদের মুখে দাঁড়িয়ে শুধু ভাত নয়, মনের ভেতর জুড়ে অন্য এক অনুসন্ধান-প্রক্রিয়া নিয়ত ক্রিয়াশীল। ‘নয়নচারা’য় যে সূচনা পরবর্তী তিন দশকের লেখালেখিতে সেই অনর্গল খোঁড়াখুড়ি। বহির্বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতি সময়ের সঙ্গে পা ফেলে ওয়ালীউল্লাহ্ আসলে খনন করে চলেন মানবমন মানবভূমি। বহির্বাস্তবকে ছাপিয়ে যায় মনোবাস্তব। ওয়ালীউল্লাহ্ তাই অন্য রকমের লেখক।
যখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কলম ধরেন—অথবা বলা ভালো, কলম ধরতে বাধ্য হন—তখন বাংলা ছোটগল্প ইতিমধ্যেই প্রায় অর্ধশতাব্দীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। এই সময়ে গল্প এক নতুন রূপ পেতে শুরু করেছে—ভাবনায়, ভাষায়, এবং নির্মাণশৈলীতে। কল্লোল যুগের ঝড় তখন থেমে গিয়েছে, কিন্তু তার ঢেউয়ে জেগে উঠেছে এক নতুন সচেতনতা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এইসব লেখক তাঁদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও বিষয়বৈচিত্র্যের দ্বারা বাংলা গল্পকে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবধর্মী জগতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। গল্পের আঙ্গিক বদলেছে দ্রুত, বদলেছে তার অন্তর্লীন বয়নকৌশল—যেখানে বাস্তবের সঙ্গে মিশেছে মনস্তত্ত্ব, সমাজচেতনার সঙ্গে আত্মসন্ধান।
জগদীশ গুপ্ত এই পরিবর্তনটিকে এক বাক্যে ধরেছিলেন—“উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয়, বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।” এই উক্তি শুধু এক লেখকের বক্তব্য নয়, যেন এক যুগের সাহিত্যদর্শন। সমাজচেতনা ও অন্তশ্চেতনার মিলনে বাংলা ছোটগল্প তখন হয়ে উঠছে বহুমাত্রিক, বৈচিত্র্যময়, এবং গভীরতর মানবিকতায় ভরপুর।
এই ধারায় একের পর এক যুক্ত হচ্ছেন নতুন লেখক—জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পর বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকের কলমে গল্প পায় মাটির গন্ধ ও মানুষের মুখ। পরবর্তী প্রজন্মে এই অনুসন্ধান চালিয়ে যান জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ—আর তাঁদেরই সহযাত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, এক ভিন্ন সুরে, এক ভিন্ন একাকিত্বে।
তাঁর প্রথম গল্প নয়নচারা-য় আমরা পাই সেই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল বাস্তবতার ছায়া, যেখানে জগদীশ ও মানিকের প্রভাব কিছুটা থাকলেও, প্রথম কয়েকটি গল্পের মধ্যেই ওয়ালীউল্লাহ্ নিজস্ব পরিসর নির্মাণ করেন। তাঁর গল্পের গঠন যেন স্থাপত্যের মতো—মজবুত, মাপা, নিখুঁত—যেখানে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি নীরবতা ইটের মতো জোড়া লাগে। তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে স্থপতির তুলনা তাই অমূলক নয়।
“সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সর্বসময়ের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখক—গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। এর মধ্যে তাঁর গল্পকার ও ঔপন্যাসিক পরিচয় বিশেষ মহত্ত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত”—এই কথাটি তাঁর সাহিত্যিক অবস্থানকে সবচেয়ে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে। ওয়ালীউল্লাহ কেবল গল্পলেখক নন, তিনি গল্পনির্মাতা। তাঁর কাছে গল্প এক নির্মাণপ্রক্রিয়া—যেখানে প্রকাশের পরও চলে ঘষামাজা, সংশোধন, পুনর্লিখন। প্রতিটি গল্প যেন তাঁর কাছে এক জীবন্ত সত্তা—অতৃপ্ত অথচ আপন।
এই অদম্য পুনর্গঠনেচ্ছা, এই সৃষ্টির প্রতি অবসেশনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর সত্যিকার লেখকসত্তা। তিনি ছিলেন নিজেরই গল্পের প্রথম পাঠক এবং সবচেয়ে নির্মম বিচারক। লেখার প্রতি এই নিষ্ঠা, এই আত্মনিবেদনই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে বাংলা গল্পের ইতিহাসে এক অনন্য স্থানে স্থাপন করেছে—যেখানে শিল্প ও জীবনের সীমারেখা মিশে গেছে এক গভীর মানবিক স্থাপত্যে।
‘নয়নচারা’ প্রকাশের কিছু বছর পর, প্রায় ১৯৪৯ নাগাদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র কলমে গল্পের গতি ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে শুরু করে। লেখক-মন চায় বৃহত্তর পরিসর—বিস্তার, গভীরতা, এবং আত্মঅন্বেষণের আরও প্রশস্ত ক্ষেত্র। তাই তাঁর দৃষ্টি গল্পের ছোট পরিসর ছেড়ে ক্রমে নিবিষ্ট হয় উপন্যাস ও নাটকে। ফলত প্রথম গল্পগ্রন্থ নয়নচারা প্রকাশের দুই দশক পরেই, ১৯৬৫ সালে, প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও শেষ গল্পসংকলন দুই তীর ও অন্যান্য গল্প। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি খোলাখুলি স্বীকার করেন নিজের লেখার প্রতি এক অনিরাময় অতৃপ্তি—“পূর্ব-প্রকাশিত গল্পগুলি এ সঙ্কলনের জন্য ঘষামাজা করেছি, নাম বদলেছি, স্থানে স্থানে লেখকের অধিকার সূত্রে বেশ অদল-বদলও করেছি।”
এই ‘ঘষামাজা’র মধ্যেই প্রকাশ পায় এক স্থপতির ধৈর্য ও সৃষ্টির প্রতি পরম দরদ। দুই দশক আগের গল্পের নাম পরিবর্তন, যেমন দুই তীর-এর পুরনো নাম ছিল ‘কালো বোরখা’, কিংবা প্রতিটি বাক্যে পুনর্গঠনের এই প্রয়াস—সবই ওয়ালীউল্লাহ্র পরিমার্জনপ্রবণ মননশীলতার প্রমাণ। তিনি শুধু গল্প লিখতেন না, গল্পকে গড়তেন, পুনর্গড়তেন—যেন নির্মাণশিল্পী নিজের স্থাপত্যে শেষ পলিশ দিচ্ছেন। তাঁর গল্পে লেখকের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করা যায়, কারণ সেখানে গল্পের চরিত্রের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে গল্পের নিজস্ব নির্মাণশৈলী—কীভাবে শব্দ, বাক্য, বর্ণনা একে অপরকে জড়িয়ে গল্পের দেহ গড়ে তুলছে, সেটিই আসল বিস্ময়।
ওয়ালীউল্লাহ্র একটি বড় সাফল্য এই যে, তিনি গল্পকথক থেকে গল্পনির্মাতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখার ভিতরে সমকাল ও বাস্তবতার অভিঘাত তীব্রভাবে কাজ করেছে, কিন্তু তিনি সেটিকে শুধু বহির্বাস্তবের প্রতিবিম্ব হিসেবে নেননি—তাকে টেনেছেন মনের গভীরে, রূপান্তর করেছেন মনোবাস্তবে। ফলে তাঁর গল্পে বাস্তব ঘটনাই রূপ নিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রার আত্মিক ব্যঞ্জনায়। নয়নচারা-র সেই চিরস্মরণীয় উচ্চারণ—“নয়নচারা গাঁয়ে কি মা’র বাড়ি?”—খিদের, ক্লান্তির, মৃত্যুর সমস্ত গ্লানি ছাপিয়ে হয়ে ওঠে মাটির প্রতি, মাতৃত্বের প্রতি, মানবিক নিবিড়তার এক অনন্ত অনুসন্ধান।
এই মানবিক অনুসন্ধানই ভিন্ন আকার পায় জাহাজি গল্পে—যেখানে সমুদ্রযাত্রা যেন জীবনেরই প্রতীক। জাহাজের নাবিক ছাত্তার একসময় বাড়ি ফেরার অনুমতি পায়; করিম সারেঙও ভাবে, “এবার শেষ হবে তার সামুদ্রিক জীবন।” কিন্তু বন্দরে পৌঁছে সে ছাত্তারের হাতে তুলে দেয় সেই আকুতিভরা ছাড়পত্র—“তুই বারিৎ যা গই, আর ন আইছ্”—আর নিজে স্থির করে, “সে আবার জাহাজে চুক্তি নেবে, আমৃত্যু সমুদ্রেই বাস করবে।” এখানে জাহাজ হয়ে ওঠে অস্তিত্বের প্রতীক—যারা ভাসমান, যাদের ঘরজীবন নেই, তাদের জন্য জাহাজই ঘর। করিম সারেং তাই সমুদ্রকেই নিজের চিরনিবাস হিসেবে মেনে নেয়।
শওকত ওসমান যথার্থই লিখেছিলেন—“ওয়ালীউল্লাহর নিসর্গবন্দনা উপন্যাসের পটভূমি নয়, বরং তা তার অলংকারবিশেষ।” তাঁর নিসর্গ কখনো পট নয়, চরিত্র। পরাজয় গল্পে প্রকৃতি যেন পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকা নিয়ে সহাবস্থান করে; বিভূতিভূষণের মতোই, কিন্তু এক ভিন্ন আবেগে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। আবার মৃত্যু-যাত্রা গল্পে মন্বন্তর নিজেই প্রধান চরিত্র—একটি মৃতদেহকে ঘিরে মানুষের ক্ষুধা, ভয়, এবং নিষ্ঠুর জীবিতাবস্থার প্রতীকায়ন। গল্পের সেই পরম বাক্য—“বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মত”—পাঠককে এক নিঃশব্দ বিস্ময়ে আবিষ্ট করে।
এভাবেই গল্প থেকে গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেকে গড়েছেন এক স্থিতধী স্থপতির মতো—যিনি প্রতিটি নির্মাণে রাখেন গভীর মমতা, কিন্তু প্রয়োজনে নির্মম শীতলতা। তুলসীগাছের কাহিনী, খুনি, দুই তীর, নিস্ফল জীবন, মৃত্যু-যাত্রা, মালেকা, সেই পৃথিবী, কেরায়া, সতীন—প্রতিটি গল্পেই তাঁর মননচর্চা কাজ করেছে শিলার মতো দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে।
অবসর কাব্য গল্পে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের জটিল মানসিক গহ্বর উন্মোচন করেন, এমন এক বুদ্ধিদীপ্ত স্বীকারোক্তি নিয়ে যা পাঠককে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়—“মধ্যবিত্তের মননে এত জটিলতা সত্যিই থাকে?” কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্বাস করতেন, মনের গভীরে এমন অন্ধকার গলি, এমন আবর্ত, এমন দ্বন্দ্বই মানুষকে মানুষ করে তোলে। এই অনুসন্ধানেই তিনি মনোবিকলনের সীমা ছুঁয়েছেন স্তন গল্পে—যেখানে মাতৃত্ব, শোক, এবং বিকারের মিশ্রণে জন্ম নেয় এক বিভীষিকাময় মানবিক মুহূর্ত। মাতৃহারা শিশুকে কোলে নেওয়া মাজেদা যখন নিজের শুকনো স্তনে দুধ খুঁজতে থাকে, তখন সেই তৃষ্ণা কেবল মায়ের নয়, সমগ্র নারীত্বের এক রক্তাক্ত আর্তি। গল্পের শেষ দৃশ্যে, যখন “তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, তবে সে-দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল”—তখন ওয়ালীউল্লাহ্ কেবল গল্প লেখেন না, তিনি মানবমনের অন্ধকারতম কক্ষে এক প্রদীপ জ্বেলে দেন।
এই নিবিড় মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, এই নিরীক্ষাধর্মী নির্মাণশৈলীই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্থায়ী এবং একক করে তুলেছে—যেখানে গল্প হয়ে ওঠে মননের প্রতিচ্ছবি, আর প্রতিটি শব্দ এক এক বিন্দু রক্ত।
ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পভুবনে এমন বহু রচনা আছে, যেগুলোর নির্মাণকৌশল পাঠককে একযোগে সচকিত ও বিস্মিত করে—যেন গল্প নয়, এক শিল্পকর্ম, যার প্রতিটি অনুচ্ছেদ গড়ে ওঠে অন্তঃস্থ কারিগরির দীপ্তিতে। না কান্দে বুবু গল্পটির প্রতিটি অনুচ্ছেদে যে সূক্ষ্ম কারুকাজ, তা প্রায় অলৌকিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথাও অনামা চরিত্রের সংলাপ, কোথাও নিঃশব্দ বর্ণনা; কোথাও বা একই বাক্য পুনরাবৃত্ত হয়েছে নানা ভঙ্গিতে—তবু পাঠক এক মুহূর্তের জন্যও ক্লান্ত হয় না। বরং এই পুনরাবৃত্তিই তৈরি করে এক রূপকথার নেশা, এক ভাষিক সংগীত, যা মনে করিয়ে দেয় গল্পও হতে পারে ছন্দের এক ভিন্নতর রূপ।
ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পের এই মোহময়তা মূলত তাঁর ভাষাবিলয়-এর জাদুতে। তাঁর কলমে ভাষা অলঙ্কার নয়, যেন নিজেই এক সুরলিপি, যার প্রতিটি শব্দে অনুরণিত হয় সৃষ্টির ছোঁয়া। যেমন নয়নচারা-য়—“আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবল।” অথবা কেরায়া-য়—“কানা বেড়ালের মতো নিঃশব্দে সতর্ক পদক্ষেপে অবশেষে ভোর আসে।” অবসর কাব্য-এ রাত্রি যেন নিজেই স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে—“পৃথিবীময় মখমলের মতো রাত্রি এসেছে নিঃশব্দে।” আবার স্বপ্নের অধ্যায়-এ অনুভূতির ভাষা—“মাস্টারনিটির সঙ্গে তার ভাব হল, পাখির পালকের মত উষ্ণ নরম ভাব।” এমনকি শিশুস্মৃতি-সিক্ত নানির বাড়ির কেল্লা-য়ও সেই কল্পনাময় নৈপুণ্য—“খানিকটা উজানে নদীটি হঠাৎ কেচ্ছার মতো রহস্যময় হয়ে গেছে।”
জীবনানন্দ বলেছিলেন, “উপমাই কবিতা।” সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গদ্যে সেই উপমাই হয়ে ওঠে কবিতার বিকল্প—যেখানে গল্পের শরীরের ভেতরেই গোপনে প্রবাহিত হয় কবিতার রক্তধারা। তাঁর গল্প পড়লে মনে হয়, তিনি যেন গদ্যের আড়ালে কবিতা লিখেছেন—শব্দের পিঠে বয়ে এনেছেন এক নীরব সংগীত, যা পাঠকের মনে চিরস্থায়ী প্রতিধ্বনি তোলে।
তবে তাঁর গল্পের আরেকটি অপরিহার্য উপাদান হলো পূর্ববঙ্গের বৈচিত্র্যময় উপভাষা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, যশোর, খুলনা, বরিশালের গন্ধ মেশা যে কথ্যভাষা—ওয়ালীউল্লাহ্ সেটিকে তুলে এনেছেন চরিত্রের ঠোঁটে ঠোঁটে, জীবনের নিখাদ স্বরে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা যেন পাতার গায়ে লেখা থাকে না; তারা উঠে দাঁড়ায়, মুখোমুখি হয়, নিঃশ্বাস ফেলে, কাঁদে, চুপ করে। এই ভাষাই তাদের শরীর ও আত্মা, আর এই উচ্চারণেই লুকিয়ে থাকে ওয়ালীউল্লাহ্র বাস্তবতার সত্য।
এই বাস্তবতা কেবল বাইরের নয়, অনেক গভীর—অন্তর্জীবনের। চরিত্রের ভেতরের মানুষটিকে উন্মোচন করাতেই তাঁর আসল স্বকীয়তা। পাঠককে তিনি এমন এক সংবেদনশীল অভ্যন্তরে টেনে নেন, যেখানে গল্পের মানুষগুলো শুধু দেখা যায় না—তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। যেন পাঠক নিজেই গল্পের এক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে, তাদের দুঃখ-হতাশা-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হয়।
বাংলা ছোটগল্পের যে প্রবহমান ধারা—যেখানে জগদীশ, মানিক ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সৃষ্টিতে আমরা তার উপস্থিতি অনুভব করলেও ঘনিষ্ঠভাবে তাকে স্পর্শ করা যায়নি—সেই ধারার এক প্রত্যক্ষ ও প্রাণময় রূপ এনে দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর গল্পসমগ্র যেন এক অনন্ত নদী—যেখানে গল্প ও ভাষা, মানুষ ও মাটি, অন্তর্জীবন ও নিসর্গ মিশে গিয়েছে অবিচ্ছিন্ন স্রোতে। একালের পাঠক এই স্রোতে দাঁড়িয়ে যেমন মুগ্ধ, তেমনই গর্বিত—কারণ ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের উপহার দিয়েছেন বাংলা গল্পের সেই আস্বাদ, যা একাধারে সৌন্দর্যের এবং আত্মগৌরবের।