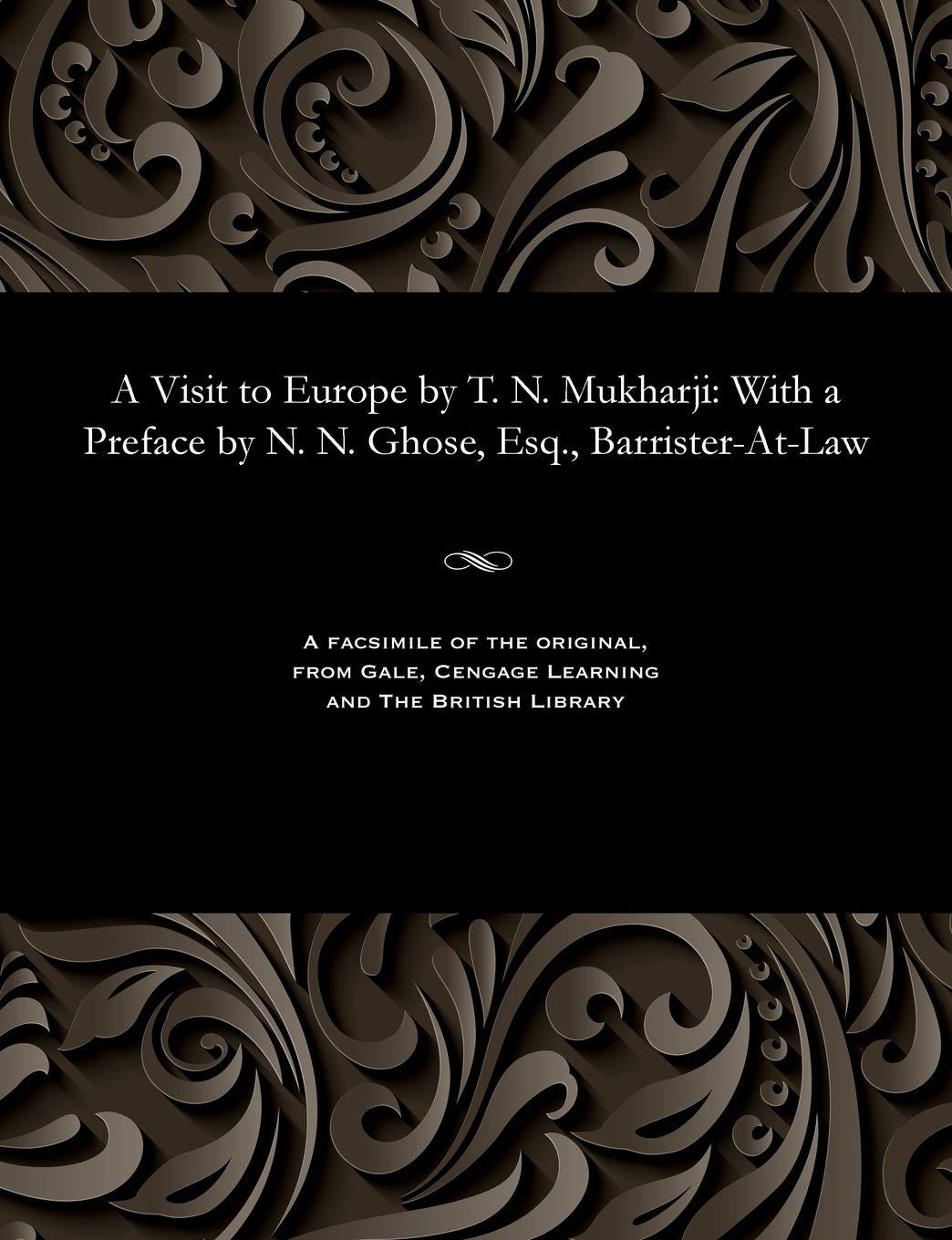ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
তাঁর রচনা-পৃথিবীতে প্রবেশ করার মানে, বাংলা সাহিত্যের সেই গলিপথে প্রবেশ করা, যেখানে দুর্বোধ্য তত্ত্ব নয়, বরং সংবেদনশীল মন ও রসবোধই নির্দেশ করে চলার পথ।
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীপঞ্জি একটি রূপকথার মতো বিস্ময়কর, কিন্তু সে বিস্ময় কোনও অলৌকিক চমকের ওপর দাঁড়িয়ে নয়—বরং দাঁড়িয়ে আছে অধ্যবসায়ের দুঃসাহসিকতায়, একধরনের বৈচিত্র্যপিপাসা ও অন্তর্গত ব্যঙ্গবোধের নিভৃত, অথচ প্রখর শক্তির ওপর। বাংলা সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ পথে হাঁটেননি তিনি, তাঁর পদচিহ্ন পড়ে আছে সেইসব অলিগলিতে, যেগুলিকে মূলধারার ইতিহাসপ্রণেতারা বহু সময় অবজ্ঞা করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন—যেন হাস্যরস কোনো গুরুগম্ভীর সাহিত্যপ্রসঙ্গের অন্তর্গত হতে পারে না, যেন রসবোধ মানেই শৃঙ্খলা-ভ্রষ্টতা। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন সেই বিরল লেখকদের একজন যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, হাসি মানে শুধু হাসাহাসি নয়—তাতে থাকে সমাজদৃষ্টি, বিদ্রুপ, নীতিকথার ছদ্মরূপ, এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি।
জন্ম ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ৬ই শ্রাবণ, ইংরেজি ১৮৪৭ সালের ২২শে জুলাই, রাহুতা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কিন্তু আর্থিকভাবে অবনমিত পরিবারে। পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের ঘরে জন্ম নেওয়া এই বালক চুঁচুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুল থেকে শুরু করে তেলিনীপাড়ার পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার জন্য কৈশোরেই তাঁকে শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে হয়—এ এক পর্বের সূচনা, যা তাঁকে শিক্ষক থেকে পুলিশ, কেরানি থেকে কিউরেটর, ভারতীয় কারুশিল্পের দূত থেকে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রতিনিধিত্বকারী একজন বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করে।
এই বহুমুখী কর্মজীবন, যেটির শুরু হয়েছিল স্কুলশিক্ষক হিসেবে দ্বারকা, উখড়া, শাহজাদপুরে, পরবর্তীতে ওড়িয়া ভাষা শেখেন এবং সম্পাদনা করেন ‘উৎকল শুভকরী’। এখানেই তাঁর পরিচয় ঘটে স্যার উইলিয়ম হান্টারের সঙ্গে—এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যা তাঁর পেশাগত যাত্রাকে এক নতুন গতিপথ দেয়। কেরানি হিসেবে বেঙ্গল গেজেটিয়ারে যোগদান, পরে কৃষি ও বাণিজ্য দপ্তরে দায়িত্ব, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোপরি শিল্পোন্নয়নমূলক গবেষণা ও বই রচনা—এইসব মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক অনন্য কর্মজীবন, যা তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়কে প্রেক্ষাপট দেয়।
কিন্তু সেই পরিচয়ই বা কম কী? "কঙ্কাবতী", "ডমরু চরিত", "পাপের পরিণাম", "নয়নচাঁদের ব্যবসা", "ফোক্কা দিগম্বর", "লুন্নু", "বীরবালা", "মজার গল্প", "জাপানের উপকথা"—ত্রৈলোক্যনাথের নাম এইসব গ্রন্থের পৃষ্ঠায় চিরস্থায়ী হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ‘কঙ্কাবতী’-র প্রশংসা করে বলেছিলেন, “এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ।” এই উক্তির মধ্যে শুধু লেখকের দক্ষতা নয়, একটি ঐতিহাসিক স্বীকৃতিও নিহিত আছে—রূপকথা, ব্যঙ্গ এবং কল্পনাপ্রবণতাকে বাংলার আধুনিক সাহিত্যভাষ্যে স্থান দেওয়ার জন্য ত্রৈলোক্যনাথই ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।
তাঁর সাহিত্যে ‘হিউমার’ যেন এক বিশেষ বর্ণমালার মতো কাজ করে, যেটা পাঠককে কেবল হাসায় না, চেতনার এক গভীর খনিতে নামিয়ে দেয়। ডমরু চরিত সেই অর্থে শুধু একটি বিদগ্ধ কৌতুক নয়—এ এক তীব্র ব্যঙ্গচর্চা, যাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের কাঠামোয় অনেকসময় অসুবিধাজনক মনে করে থাকি, অথচ এই টেক্সটটিই প্রমাণ করে দেয় যে কীভাবে কল্পনার চূড়ান্ত বিকাশ ব্যঙ্গকে দর্শনে পরিণত করতে পারে।
ত্রৈলোক্যনাথের আরেকটি আশ্চর্যদর্শন দিক ছিল তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি। ইউরোপ ভ্রমণের পরে রচিত তাঁর “A Visit to Europe” গ্রন্থটি এক অর্থে ঔপনিবেশিক গণ্ডিকে অতিক্রম করার এক মানসিক প্রয়াস, যেখানে ভারতীয় এক শিক্ষিত ব্যক্তি বিদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পর্যালোচনা করছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও রসবোধের মধ্য দিয়ে। আবার তাঁর “Art Manufactures of India” অথবা “Descriptive Catalogue of Indian Products” প্রমাণ করে, যে তিনি শুধু গল্প বলতেন না, বরং দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্যকে এক ছকে বাঁধার জন্য ব্যুৎপত্তির সঙ্গে ভাষার দখল কাজে লাগাতেন।
বাংলা বিশ্বকোষের সূচনাপর্বেও তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে এ প্রকল্পে কাজ করেন তিনি, যা বাংলা জ্ঞানচর্চার পরিধিকে গভীরতর করে। পাশাপাশি 'জন্মভূমি', 'Wealth of India'-র মতো পত্রিকাতেও তাঁর রচনার বাহার ছড়িয়েছিল। তিনি ছিলেন একাধারে প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পতাত্ত্বিক, রম্যরচয়িতা এবং সাহিত্যের ফ্যান্টাসি-উদ্ভাবক।
এবং এই বিস্ময়কর বহুবর্ণতা হয়তো তাঁরই যুগে এক ধরনের নির্জনতা বয়ে এনেছিল। হয়তো এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে প্রান্তিক এক চরিত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বহুদিন। কিন্তু আজ, যখন আমরা হাস্যরসের মধ্যেও রাজনৈতিকতা, ফ্যান্টাসির মধ্যে ঐতিহ্যের বিকাশ এবং প্রবাসজীবনের বিবরণেও ভাষার শৈল্পিক সম্ভাবনা খুঁজে পাই—তখন ত্রৈলোক্যনাথ যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্য নতুনভাবে আলোচিত হবার দাবি রাখে।
১৯১৯ সালের ১১ই মার্চ, মাত্র ৭৩ বছর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথ প্রয়াত হন। কিন্তু প্রয়াণ তাঁর সমাপ্তি নয়। কঙ্কাবতীর শতবর্ষীয় পথচলা কিংবা ডমরু চরিতের অপূর্ব পাঠকপ্রিয়তা আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এক সাহসী ব্যতিক্রমী কণ্ঠ কতভাবেই না সাহিত্যের মঞ্চকে সমৃদ্ধ করে। হাস্যরসের এই মহান কথাকার—যিনি সমাজকে দেখেছেন বিদ্রুপের চশমা পরেও গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে—তাঁকে আমরা কীভাবে মনে রাখি, সেটাই এখনকার সাহিত্যের এক আত্মজিজ্ঞাসার বিষয়।
তাঁর রচনা-পৃথিবীতে প্রবেশ করার মানে, বাংলা সাহিত্যের সেই গলিপথে প্রবেশ করা, যেখানে দুর্বোধ্য তত্ত্ব নয়, বরং সংবেদনশীল মন ও রসবোধই নির্দেশ করে চলার পথ। আর সেই পথ একবার ধরতে পারলে, একশো বছর পরে দাঁড়িয়েও, পাঠক বুঝবেন—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখক কোনো সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েন না। তিনি আমাদের চিরকালীন।