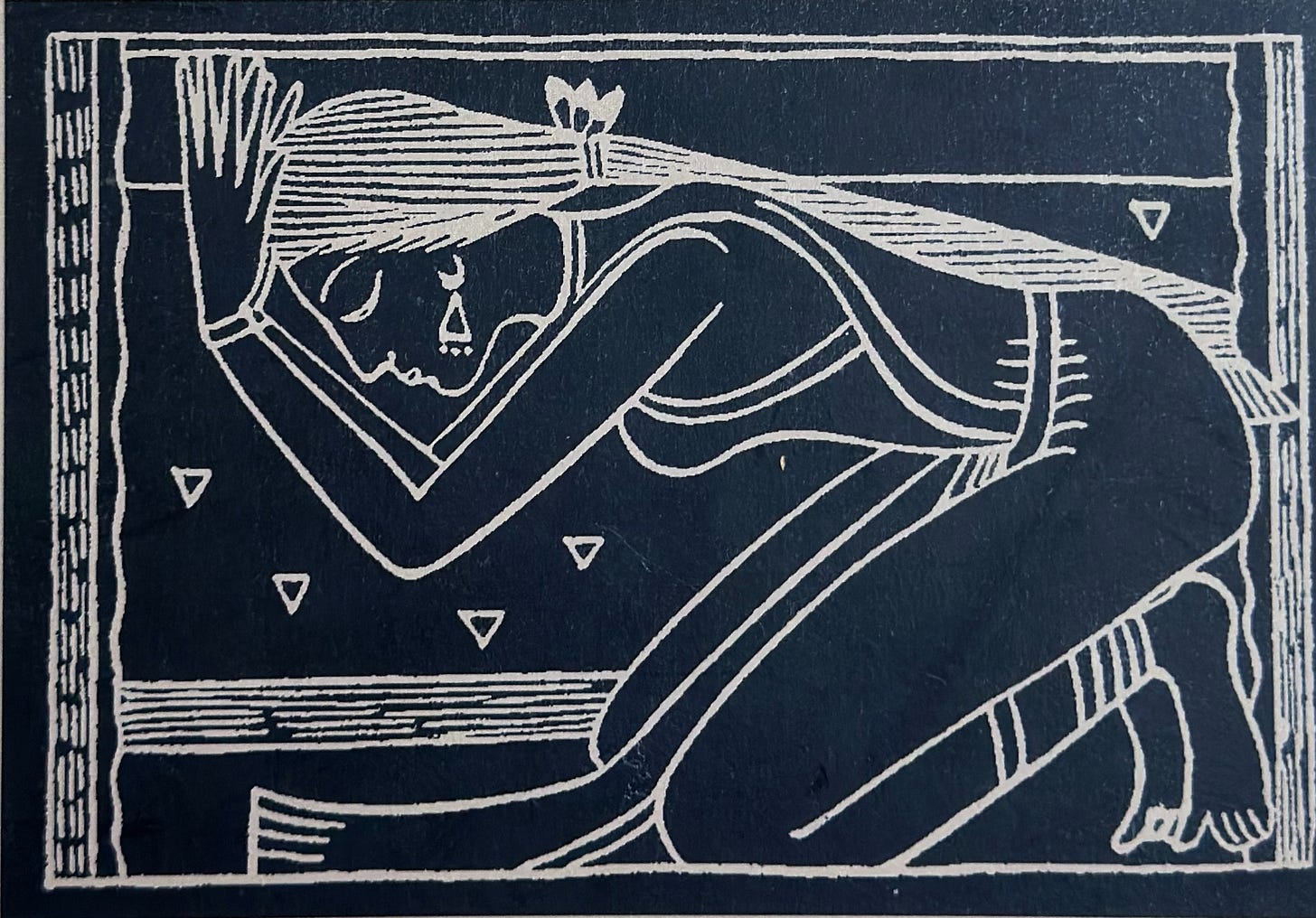সাহিত্যের দেহ ও আত্মা
কখনো হৃদয়ের অন্দর থেকে উঠে আসে রসের প্রবাহ, কখনো বাস্তবের রুক্ষ পাথরে গড়ে ওঠে সাহিত্যিক নির্মাণ—তবু দেহ ও আত্মার এই দ্বৈত সঙ্গেই গঠিত হয় সেই রচনা, যা কালের কণ্ঠে টিকে থাকে।
কখনো হৃদয়ের অন্দর থেকে উঠে আসে রসের প্রবাহ, কখনো বাস্তবের রুক্ষ পাথরে গড়ে ওঠে সাহিত্যিক নির্মাণ—তবু দেহ ও আত্মার এই দ্বৈত সঙ্গেই গঠিত হয় সেই রচনা, যা কালের কণ্ঠে টিকে থাকে। এই লেখায় আমি অনুসরণ করেছি সেই পথ, যেখানে ‘খাঁটি’ ও ‘মিশ্র’, ‘আদর্শবাদ’ ও ‘বাস্তববাদ’—সবাই এক মঞ্চে, এক বিরল নাট্যে মুখোমুখি।
রিটন খান
যা কিছু লেখা—তা-ই কি সাহিত্য? শুনলে যেন মনে হয়, কলম চালালেই সাহিত্য জন্ম নেয়। সেই হিসাবে তো হিসাববিজ্ঞানও সাহিত্য, রসায়নের রচনাও—কিন্তু আমরা জানি, তা নয়। আসলে সাহিত্য এক বিশেষ জাতের রচনা, সব লেখা তার আওতায় পড়ে না। তফাৎটা ঠিক কোথায়? সাহিত্যের জন্ম হয় মানুষের হৃৎস্পন্দনের ভিতর দিয়ে—সুখ-দুঃখ, বাসনা-ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন আর সংকটের অলিন্দ ঘুরে, সে ভাষা পায় আবেগের। আর অ-সাহিত্য? সে তথ্যের বর্ণনা, ব্যাখ্যার শরীর; অনুভূতির সঙ্গে যার যোগাযোগ নেই—সে যেন হৃদয়ের বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক কোলাহলহীন বক্তা। তাই সাহিত্য মানে ভাবাত্মক রচনা—যেমন কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস কিংবা কোনো অনুভবজাত প্রবন্ধ। আর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যাকরণ? তারা তাদের নিজস্ব পথে হাঁটে, বিষয়ভিত্তিক রচনার নামে পরিচিত হয়, কিন্তু সাহিত্যের ঘরে ঢোকার অনুমতি মেলে না তাদের। তারা নির্মমভাবে অ-সাহিত্য—আবেগে নয়, তথ্যের ঘাম ঝরানো এক নিরুত্তাপ নির্মাণ।
সাহিত্যকে মোটামুটি পাঁচটি ধারায় ভাগ করা যায়—কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প আর হৃদয়াবেগে ভেজা প্রবন্ধ। আজ আমরা এদের আলাদা আলাদা পরিচয়ে ডাকি, কিন্তু প্রাচীন রসবিশারদদের কাছে এরা সবাই ছিল এক গোত্রের, এক নামে—‘কাব্য’। ভাবুন একবার, কবিতা থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে গল্প, সব কিছুই ছিল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। তারা আবার এ কাব্যকে টুকরো টুকরো করে নাম দিয়েছিল—শ্রব্য কাব্য মানে কবিতা, দৃশ্য কাব্য মানে নাটক, গদ্য কাব্য মানে উপন্যাস, আর গাথা বা চম্পু কাব্য যাকে বলি গল্প কিংবা উপকথা।
আজকের দিনে এই বিভাজন খানিকটা বেশি গুছানো, বুঝতেও সুবিধে। তবে প্রাচীনেরা কেন এত রচনাকে একই ‘কাব্য’ ছাতার নিচে ফেলেছিলেন? কারণ ছিল গভীর। আকারে বা কাঠামোয় যত পার্থক্য থাক, এসব রচনার উৎস একটাই—লেখকের মন। আর উদ্দেশ্যও অভিন্ন—পাঠকের চিত্তে আবেগের ঢেউ তোলা। এক হৃদয়ের ভিতরকার আন্দোলন বহু হৃদয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার নামই সাহিত্য, আর সেই আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াই তো আসলে কাব্য। এই ভাবেই, একরকম আত্মীয়তার খোঁজে, প্রাচীন মনীষীরা সব সাহিত্যকেই কাব্য বলে ডাকতেন—মনে করতেন, এ এক অভিন্ন আত্মা, কেবল রূপ বদলেছে।
তবে সাহিত্যের আসল লক্ষণটা কোথায়? আগেই বলা হয়েছে—সাহিত্য জন্মায় মানুষের অন্তরের জমিনে, যেখানে বোনা থাকে সুখের ছায়া, দুঃখের কাঁটা, আশার আলো, আর হতাশার ছায়াপথ। একজন লেখক যখন সেই জমিতে নিজের অভিজ্ঞতার বীজ রোপণ করেন, তখন বহু পাঠকের হৃদয় সেই অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি খুঁজে পায়। এই মিলনটাই তো সাহিত্যের আসল যাদু—লেখকের চেতনার সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের নীরব মৈত্রী।
কিন্তু এই সংযোগটা ঘটে কীভাবে? আমরা প্রতিদিন তো কত কিছু দেখি—টেলিভিশনের সংবাদের ঝলক, কাগজের পাতায় ঘটনাপুঞ্জ, বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টের পাহাড়। তবু, একটা গল্প পড়লে, কিংবা মঞ্চে একটা নাটক দেখলে যে অনুভূতির ঢেউ ওঠে মনে, সেটা কোথা থেকে আসে? কেন আসে? কারণ, সেখানেই থাকে সাহিত্যের অতিরিক্ত রস—যেটা সংবাদে নেই, ঘোষণায় নেই, বিবরণে নেই।
এই রস—মানে কেবল ‘মিষ্টি’ নয়, বরং সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার রঙ যা লেখক তার ভাষায় মিশিয়ে দেন, পাঠকের অনুভবে ঢেলে দেন। সাহিত্যের প্রাণ ওই রসেই, যা না থাকলে রচনাটা যেমনই হোক, তা পাঠককে ছুঁতে পারে না, স্পর্শ করতে পারে না। কেবল তথ্য নয়, সাহিত্য আসলে সেই আত্মার আরতি, যেটা পাঠকের চিত্তে আলো জ্বালাতে পারে।
অলঙ্কার শাস্ত্র বলে, রসের সংখ্যা নয়টি—একেকটা যেন মানুষের মনের একেকটি স্বরলিপি। তার মধ্যে প্রেমের রস, যাকে বলে ‘আদি’, আর ব্যথার রস, মানে ‘করুণ’, আবার আছে ‘রৌদ্র’ রস যা জাগায় তীব্র ক্রোধ, ‘শান্ত’ রস যা আনয়ন করে চিত্তের প্রশান্তি। ‘বীভৎস’ রসে জেগে ওঠে ঘৃণা, ‘অদ্ভুত’ রসে খেলে যায় বিস্ময়। সব মিলিয়ে, রসের কাজ মূলত একটাই—হৃদয়ে বিশেষ কোনো অনুভূতির সঞ্চার ঘটানো।
কিন্তু এই আবেগ আসে কোথা থেকে? রস তো জাদু নয়—তার পেছনে আছে দৃশ্য, ভাষা, আর এক সূক্ষ্ম নির্মাণ। ধরুন, একজন লেখক একটি দরিদ্র বিধবার একমাত্র ছেলের মৃত্যু বর্ণনা করছেন—তাঁর কান্না, নিঃস্বতা, আর নিঃসঙ্গতার মর্মর ধ্বনি। এই চিত্র যখন পাঠকের চোখে আসে, তখন তার হৃদয় কাঁপে। এটা আর নিছক তথ্য নয়, কাগজে ছাপা সংবাদ নয়—এ এক অনুভূতির স্থানান্তর।
এই অনুভূতির রস যদি না জন্মায়, তাহলে সেটা হয়ে যায় একখানি বিবরণ—নিরস, নিরাবেগ, আর সাহিত্যের উঠোনে যার কোনো জায়গা নেই। সাহিত্য কেবল গল্প বলার জায়গা নয়, তা হলো সেই অনুভব-যন্ত্র, যা পাঠকের ভেতরের তারে হাত রাখে। রস-হীন রচনা কেবল ভাষার কঙ্কাল; প্রাণ তো তাতে তখনই আসে, যখন রস এসে তাকে ভিজিয়ে দেয়।
এই যে ‘রসাত্মকতা’—মানে হৃদয়-ছোঁয়া আবেগের রঙ, এটাই তো সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাস্তবের কাগজ খুলে দেখা যায়, ‘সাহিত্য’ নামে যা কিছু লিখিত হচ্ছে, তার সবকিছুতে এই রসের পরশ মেলে না। অনেক গল্প, উপন্যাস, নাটকে যতটা না অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, তার চেয়ে ঢের বেশি থাকে চিন্তা, মতবাদ, তত্ত্ব আর বিশ্লেষণের ভার। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি—সব উঠে আসে, কিন্তু আবেগপ্লাবিত ভাষা নয়, সেখানে বুদ্ধির অনুশীলন চলে। কবিতাতেও এমন দেখা যায়—ভাব আছে, ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকে তত্ত্ব বা মতপ্রকাশের গরল।
এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে—এসব রচনা সাহিত্য কিনা? খাঁটি অলঙ্কার শাস্ত্রের চোখে দেখলে এগুলো ‘বিশুদ্ধ সাহিত্য’ নয়—বরং ‘মিশ্র সাহিত্য’। মানে, এখানে সাহিত্য ও অ-সাহিত্যের উপাদান একসঙ্গে খিচুড়ির মতো জড়ো হয়েছে। রসতত্ত্বের কষাগুণ মেপে বললে, কেবল নিখাদ লিরিক কবিতাকেই ‘বিশুদ্ধ সাহিত্য’ বলা চলে।
কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখি? সাহিত্যের মহাজনরাই তো নানা দার্শনিকতা, তথ্য, মত আর আদর্শ নিয়ে খেলেন। নিছক রস নয়—তত্ত্বও তাঁদের লেখায় ঢুকে পড়ে। ফলে ‘মিশ্র সাহিত্য’ই আসলে সাহিত্যের বাস্তব রূপ। বিশুদ্ধ সাহিত্য হয়ও কম, আর হলেও আদৌ তা দরকারি কিনা, তা নিয়েও দ্বিধা আছে।
এই দ্বিধা থেকেই নতুন প্রশ্ন জন্মায়—সাহিত্যের প্রয়োজনটাই বা কী? একদল আদর্শবাদী বলেন, সাহিত্য মানুষকে জীবনের দুঃখ-গ্লানি ভুলিয়ে, তাকে এক নির্মল উচ্চতায় তুলে ধরার শিল্প। তারা মনে করেন, সাহিত্য যেন স্বর্গের জানালা—যেখানে কল্পনার আলো এসে পড়ে রক্তমাংসের জীবনে। এই ভাবধারাকেই বলা হয় idealism।
অন্যদিকে বাস্তববাদীরা তিরস্কার করে বলেন, ওই কল্পনাবিলাস আসলে বাস্তব থেকে পলায়নের আরেক নাম। সাহিত্যকে তারা টেনে আনেন জীবনের কাদায়—বলে, বাস্তবের গন্ধ না থাকলে লেখা কেবল বাতাসে গাঁথা ফুলমালা। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জীর্ণতা—সবদিক তুলে ধরতে হবে সাহিত্যে। কারণ, শুধু পুষ্প নয়, পাঁকও সত্য—এবং বহু মানুষ সেই পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাদের উদ্ধার করাই লেখকের কাজ—এই হল বাস্তববাদীদের জোরালো দাবি।
তাহলে সাহিত্যে কোন রচনাকে ঠাঁই দেওয়া হবে আর কোনটিকে নয়, এই প্রশ্নটাই অর্থহীন। মতদ্বন্দ্ব থাকতে পারে—থাকে—তবু একটা বিষয়ে দ্বিমত নেই: সাহিত্য মানুষের জীবনেরই ফসল। এক সময় বলা হতো ‘শিল্পের জন্যেই শিল্প’, কিন্তু আজ আর সে কথা কেউ তেমন গর্ব করে বলেন না।
অনেকেই মনে করেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আটকে থাকে না। যুগ পাল্টে যায়, সমাজ বদলায়, রাজনীতির পালা ঘুরে যায়, তবু মানুষের হৃদয় যে ছায়ার ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে—ভালোবাসা, দুঃখ, বিস্ময়, ভয়—সেগুলোর মৌলিক রূপ অদলবদল হয় না। কারণ সাহিত্য জন্মায় ওই আবেগ থেকেই—এইজন্যেই তার আবেদন সময়-নিরপেক্ষ, চিরন্তন। হোমার থেকে শেক্সপিয়ার, ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—সবাই সে প্রমাণ রাখেন।
তবে এর প্রতিবাদও আছে। কেউ কেউ বলেন, মানব-মন তো বাস্তবতার ধারক। সমাজ পাল্টালে মানসিকতাও পাল্টায়। আজ যে অনুভূতি অর্থবহ, কাল তা হাস্যকর বা অচল হয়ে যেতে পারে। অতএব, সাহিত্যও ততোদিনই প্রাসঙ্গিক, যতদিন তার জন্মের বাস্তবতা প্রাসঙ্গিক। অতীত সমাজ হারালে, তার সাহিত্যের রংও ফিকে হয়। তবু অতীত সাহিত্যকে আমরা যে শ্রদ্ধা করি, তার একটা কারণ হতে পারে অভ্যস্ত সংস্কার, আর আরেকটা—তার শিল্পের সৌন্দর্য, যা সময়-সাপেক্ষে হলেও, মুগ্ধ করে।
বাস্তববাদীরা বলেন—এই শিল্প-কৌশলের সৌন্দর্য তুচ্ছ। তারা সাহিত্যকে বিচার করেন ‘প্রয়োজন’-এর চোখে। কিন্তু যে-কোনো সাহিত্যকে বুঝতে গেলে একটা সহজ সত্য স্বীকার করতেই হবে—রস হল সাহিত্যের আত্মা, আর ভাষা ও বিন্যাস তার শরীর। দেহ আর প্রাণ, এই দুইয়ের সম্মিলনেই উচ্চমানের সাহিত্য রচিত হয়।
তবে সব লেখক এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন না। কেউ কেউ ‘মর্ম’ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, শব্দকে পাত্তা দেন না। আবার কেউ শব্দে-ছন্দে মুগ্ধ হয়ে লেখেন, অথচ অনুভবের রস ফাঁকা থেকে যায়। ফল কী? প্রথম দলের রচনা হয়তো সম্মান পায়, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে বসতে পারে না। আর দ্বিতীয় দলের লেখায় বাহার থাকে, শব্দে আলো ঝলমল, পাঠক করতালি দেয়—কিন্তু সময়ের প্রবাহে তা ফিকে হয়ে যায়।
চিরস্থায়ী সাহিত্য একটাই—যেখানে দেহ আর আত্মা, ফর্ম আর কনটেন্ট, ভাব আর ভাষা, একই ছাদের নিচে বাস করে। প্রাচীন হোক বা আধুনিক, যে রচনাগুলো আমাদের বারবার টানে, তাদের ভেতর এই সুষম মেলবন্ধন অনিবার্যভাবেই থাকে।