ফকনার পাঠ
সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন তাঁর সারা জীবন পূর্ণিয়ার পরিবেশ এবং সেখানকার মানুষজন নিয়ে লিখেছেন, তেমনি ফকনারও তাঁর নিজস্ব একটি অঞ্চলের গল্প নিয়ে লিখে গেছেন।
ফকনার পাঠ
রিটন খান
ফকনার পড়া শুরু করতে চাইলে A Rose for Emily (এমিলির জন্য গোলাপ) একটি চমৎকার গল্প । গল্পটি জেফারসন, মিসিসিপি নামের একটি কল্পিত শহরে ঘটা এটি দক্ষিণী গথিক ধাঁচের। সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন তাঁর সারা জীবন পূর্ণিয়ার পরিবেশ এবং সেখানকার মানুষজন নিয়ে লিখেছেন, তেমনি ফকনারও তাঁর নিজস্ব একটি অঞ্চলের গল্প নিয়ে লিখে গেছেন। ফকনারের সেই কল্পিত অঞ্চলটির নাম ‘ইয়োকনাপাটাওফা কাউন্টি’। এই অঞ্চলের সাদা, কালো ও বাদামী মানুষের জীবনকাহিনি তিনি তুলে ধরেছেন একের পর এক উপন্যাসে—‘স্যারকুচয়ারি’, ‘লাইট ইন অগাস্ট’, ‘দ্য আনভ্যাংকুইল্ড’, ‘দ্য হ্যামলেট’, ‘গো ডাউন মোজেজ’। আঞ্চলিক হওয়া সত্ত্বেও ফকনারের এই রচনাগুলি বৈশ্বিক আবেদন নিয়ে সমকালীন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও তিনি বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন, তবু জনপ্রিয়তার স্বাদ সেভাবে পাননি। জীবনের একটি সময়ে তাঁর বইয়ের বিক্রি তলানিতে ঠেকে, এমনকি প্রকাশকরাও মুখ ফিরিয়ে নেন। চল্লিশের দশকের গোড়ায় ফকনার প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে একটিমাত্র বই পাওয়া যেত, বাকিগুলি অদৃশ্য। তবে ফকনারের সৌভাগ্য, জীবদ্দশাতেই তিনি পুনরাবিষ্কৃত হন। রবার্ট পেন ওয়ারেনের মতো তরুণ লেখকরা তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করেন। এর ফলে বড় প্রকাশনা সংস্থা র্যান্ডম হাউস তাঁর পুরনো বইগুলি পুনরায় মুদ্রণ করতে শুরু করে। পুরস্কারও আসতে থাকে একের পর এক।
‘এমিলির জন্য গোলাপ’ সহজ মনে হলেও গল্পটি চিন্তার খোরাক জোগায়। প্রথাগত ধারার বাইরে লেখা এই গল্প শুরু হয় এমিলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দৃশ্যে এবং অতীতের ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে সামনে এনে এক চমকপ্রদ পরিণতিতে শেষ হয়। পাঠকদের জন্য এটি এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
উইলিয়াম ফকনার কখনো তার লেখায় কালানুক্রমিকতার বাঁধনে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি গল্পটিকে প্রথাগত ধারার বাইরে ধীরে ধীরে চরিত্রগুলোর গভীরতা এবং মিস এমিলি ও তার দুর্গন্ধময় বাড়ির রহস্য উন্মোচনের কৌশল বেছে নেন। গল্পের প্রথম অংশেই মৃত্যু-চিত্রের প্রাধান্য স্পষ্ট। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রসঙ্গ তো আছেই, কিন্তু যখন ওয়ার্ড কমিশনাররা এমিলির বাড়িতে যায়, তখন তার বর্ণনা আরও মৃত্যুচিহ্ন বহন করে। ফকনার লিখেছেন, ‘এমিলি ভারী শরীরের হলেও তার কাঠামোটি ছোট—জলের নিচে দীর্ঘদিন ডুবে থাকা দেহের মতো ফুলে ওঠা’।
গল্পের একটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত থেকে আমরা জানতে পারি যে একসময় এমিলি তার বাড়িতে চীনামাটির কারুকাজ আঁকার ক্লাস নিতেন, যা তার একসময়ের সামাজিক জীবনের ইঙ্গিত দেয়। এই তথ্য গল্পে পরে ফিরে আসে, এবং ফকনার এটিকে সময়ের প্রবাহ বোঝানোর একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
গল্পের শুরুতে আমরা এমিলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচিত হই এবং ধীরে ধীরে তার জীবনের খুঁটিনাটি জানি। তার বাবার মৃত্যু হয় যখন তার বয়স ত্রিশ, পরিবারে তিনিই ছিলেন শেষ উত্তরাধিকারী। তার নামে কেবল বাড়িটিই ছিল। স্থানীয় মেয়র তার প্রতি করুণা প্রকাশ করে তার বাড়ির কর মওকুফ করেন।
ক্ষমতার পালাবদলে পরবর্তীতে পরিবারটি কর দিতে বাধ্য হয়। শহরের কমিশনার কর আদায়ের চেষ্টা করলেও এমিলি সেগুলো উপেক্ষা করেন।
এমিলির একজন প্রিয় মানুষ ছিল, যার নাম হোমার। একসময় হোমার চলে যান, কিন্তু কিছুদিন পরেই তার বাড়ি থেকে ভয়াবহ দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করে, যা নিয়ে শহরবাসী অভিযোগ তোলে। এরপর থেকে এমিলিকে খুব কমই দেখা যেত। মাঝে মধ্যে তিনি চীনামাটির কারুকাজ আঁকা শেখাতেন। তখন তিনি বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, আর তার চুল রূপালী ধূসর রঙ ধারণ করেছিল।
এমিলির মৃত্যুর পর, লোকজন তার বাড়িতে ঢুকে দেখার চেষ্টা করে এত বছর ধরে তিনি কী লুকিয়ে রেখেছিলেন। বাড়ির একটি বন্ধ ঘরে তারা হোমারের কঙ্কাল আবিষ্কার করে। তার মাথার পাশের বালিশে মেলে এমিলির ধূসর চুলের একটি গোছা। অনুমান করা হয়, এমিলি হোমারকে হত্যা করেছিলেন এবং তারপর বহু বছর ধরে তার মৃতদেহের পাশে ঘুমিয়েছেন। এমিলির চরিত্রকে পুরোনো দক্ষিণ অঙ্গরাজ্যের একটি রূপক হিসেবে দেখা যেতে পারে—একটি সংস্কৃতি, যা তার নিজস্ব ঐতিহ্যে আঁকড়ে থাকতে চায়, কিন্তু অবশেষে পচে যায় এবং মৃত্যু ঘটে, নতুন কিছুর জন্য জায়গা করে দেয়। খেয়াল করে দেখবেন, গল্পের নামের “গোলাপ” কখনোই সরাসরি গল্পে উপস্থিত হয় না।
গল্পটি নিজেই হয়তো ফকনারের প্রতীকী গোলাপ, যা তিনি অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নিবেদন করেছেন।
মূল গল্প
এমিলির জন্য গোলাপ
উইলিয়াম ফকনার
ভাষান্তর: রিটন খান
১৯৪৯ সালে নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় উইলিয়াম ফকনার বলেছিলেন, মানুষ শুধু সহ্য করবে না, সে জয়ও করবে। তার সকল রচনাই মানুষের যন্ত্রণায় ভরা জীবন, ব্যর্থতা এবং অসম্পূর্ণতার কাহিনি।
মিস এমিলি গ্রিয়ারসনের মৃত্যুতে পুরো শহরের মানুষ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ছুটে গিয়েছিল। পুরুষেরা এসেছিল ভগ্ন স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাতে, আর নারীরা এসেছিল এমিলির বাড়ির ভেতরটা দেখার আগ্রহে। গত দশ বছরে বাড়ির ভেতরে কেউ ঢোকেনি, একমাত্র একজন পুরোনো চাকর ছাড়া, যিনি একসঙ্গে বাগানের মালী এবং রান্নাঘরের পাচক ছিলেন। বিশাল বাড়িটি একসময় সাদা রঙে জ্বলজ্বল করত, গোল গম্বুজ ও আকাশ-ছোঁয়া চূড়াগুলোর সঙ্গে ছিল ঝুলন্ত বারান্দা, যা এখন পরিত্যক্ত ও বিবর্ণ কাগজের মতো ঝরে পড়ার অপেক্ষায়।
বাড়িটির নির্মাণশৈলী ভারিক্কী হলেও ঠুনকো। একসময় এটি ছিল শহরের সবচেয়ে অভিজাত পাড়ার অংশ, কিন্তু এখন মোটর গ্যারেজ আর কার্পাস তুলো মাড়াইয়ের মেশিন সেই এলাকার স্মরণীয় ঐতিহ্যকে মুছে দিয়েছে। কার্পাস তুলোর ওয়াগন আর পেট্রল পাম্পের ভিড়ে মিস এমিলির বাড়ি একা দাঁড়িয়ে আছে, যেন অবাধ্য, জেদী কোনো ভাঙাচোরা শরীর। পাম্পগুলো যেন সেই বাড়ির প্রতি উপহাস ছুঁড়ে দিচ্ছে।
এখন, সিডারের ছায়ায় যেখানে জেফারসনের যুদ্ধে দুই পক্ষের নিহত অজ্ঞাত সৈন্যরা শুয়ে আছে, তাদের পদমর্যাদা জানা থাকলেও নাম অজানা—সেই স্মৃতিস্তম্ভদের পাশে মিস এমিলিও শুয়ে থাকবেন, একসময়ের সেই স্মরণীয় নামগুলোর শেষ প্রতিনিধি হিসেবে।
বহু বছর ধরে মিস এমিলি আমাদের শহরের ঐতিহ্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতীক হয়ে ছিলেন। এই দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন ১৮৯৪ সালে শহরের মেয়র কর্ণেল সারটোরিস। তিনিই প্রথম নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, কোনো নিগ্রো মেয়ে অ্যাপ্রন ছাড়া রাস্তায় বের হতে পারবে না। একই ব্যক্তি ঘোষণা করেছিলেন, মিস এমিলিকে তাঁর জীবদ্দশায় কোনো কর দিতে হবে না। তাঁর বাবা শহরের পৌর-কর্তৃপক্ষকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, এবং কর্ণেল সারটোরিস এমন একটি গল্প গড়ে তুলেছিলেন যাতে দেখানো হয়, শহর সেই ঋণের বিনিময়ে কর মওকুফের মাধ্যমে টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে।
কর্ণেল সারটোরিসের যুগের মানুষই এমন অদ্ভুত গল্প রচনা করতে পারতেন। আর একজন নারী ছাড়া আর কে-ই বা এমন কিছু বিশ্বাস করত? তবু মিস এমিলি কখনো করুণার পাত্রী হতে চাননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে কর্ণেল সারটোরিস যা বলেছেন, সেটাই সত্য।
নতুন যুগের আধুনিক চিন্তাধারা এসে পরিস্থিতি বদলে দিল। নতুন মেয়র আর কমিশনাররা কর মওকুফের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। বছরের শুরুতেই মিস এমিলিকে ট্যাক্সের নোটিশ পাঠানো হল। ফেব্রুয়ারি মাস কেটে গেল, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। এরপর তাঁকে আরেকটি চিঠি পাঠিয়ে শেরিফের অফিসে সুবিধামতো সময়ে দেখা করতে বলা হল। সপ্তাহখানেক পর মেয়র নিজেই লিখলেন—তিনি কি এমিলির বাড়িতে যাবেন, নাকি গাড়ি পাঠালে মিস এমিলি আসবেন?
উত্তর এল এক সেকেলে, অদ্ভুত ধরণের কাগজে—অস্পষ্ট কালিতে সরু ফুলকাটা অক্ষরে লেখা। মিস এমিলি জানালেন, তিনি এখন বাড়ির বাইরে যান না। সঙ্গে ট্যাক্স-নোটিশটি কোনো মন্তব্য ছাড়াই ফেরত পাঠানো হয়েছে।
কমিশনারদের স্পেশাল মিটিং ডাকা হল, এবং এক প্রতিনিধি দল মিস এমিলির সঙ্গে দেখা করতে গেল। আট-দশ বছর আগে যখন তিনি চীনামাটির কারুকাজ আঁকার ক্লাস নিতেন, সেই ক্লাস বন্ধ হওয়ার পর থেকে আর কেউ তার বাড়িতে ঢোকেনি।
প্রবেশের জন্য দরজা খুলল বৃদ্ধ নিগ্রো চাকর। ভেতরে সিঁড়ি উঠে গেছে গাঢ় ছায়ার দিকে। ঘরে ভরা বন্ধ ঘরের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ধুলো এবং অব্যবহৃত আসবাবপত্রের ছাপ। হলঘরের আবছা আলোতে সবকিছু যেন সময়ের স্তব্ধতার সাক্ষী।
নিগ্রো চাকর অতিথিদের বসার ঘরে নিয়ে গেল। ভারী চামড়ায় মোড়া আসবাবপত্র ছিল সেখানে, তবে চামড়ায় ফাটল ধরে গেছে। অতিথিরা বসার পর সূর্যের কিরণে ধুলো কণাগুলো নিঃসঙ্গ অণুর মতো ঘুরছিল। ঘরের দেয়ালে মিস এমিলির বাবার একটি ছবি টাঙানো ছিল, রঙিন খড়ি ও পেন্সিলে আঁকা।
এমিলি ঘরে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। বেঁটে-মোটা, কালো পোশাকে আবৃত মহিলার কোমরে সোনার চেন বেল্টের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। হাতের আবলুশ কাঠের ছড়ি সোনার বাঁধানো মাথা থেকে ময়লা হয়ে গেছে। তার শরীরের হাড় এত সরু যে গোলগাল মনে হওয়ার বদলে তাকে বেঢপ মোটা দেখায়। তার চোখেমুখে ফোলা ভাব, যেন স্রোতহীন জলে ডুবে থাকা এক মৃতদেহ। চামড়ার ফ্যাকাশে রঙে যেন দীর্ঘ সময়ের ক্ষয়চিহ্ন ফুটে উঠেছে। চর্বির স্তরে ঢাকা মুখে তার চোখ দুটি যেন হারিয়ে গেছে, ঠিক যেন ময়দার ঢেলার মধ্যে দুটি জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।
এমিলি ওদের বসতে বলেনি, দরজায় দাঁড়িয়েই চুপ করে শুনছিল। কমিশনার কথা বলতে গিয়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছিলেন, একসময় থেমে গেলেন। তখনই শুনতে পাওয়া গেল এমিলির পোষাকের আড়ালে সোনার চেনের প্রান্তে ঘড়ির টিকটিক শব্দ।
“জেফারসনে আমি কোনো ট্যাক্স দিই না,” শুকনো, ঠাণ্ডা গলায় বললেন এমিলি। “কর্ণেল সারটোরিস আমাকে জানিয়েছিলেন, আমার কোনো ট্যাক্স বাকি নেই। সিটি রেকর্ডস দেখলেই আপনারা তা জানতে পারবেন।”
“আমরা দেখেছি, মিস এমিলি। আমরা শহরের নতুন প্রশাসক। আপনি কি শেরিফের নোটিশ পাননি?”
“হ্যাঁ, কিছু কাগজ পাঠানো হয়েছে। যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি হয়তো নিজেকে শেরিফ ভাবেন। কিন্তু জেফারসনে আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় না।”
“কিন্তু রেকর্ডে এ ধরনের কোনো উল্লেখ নেই। আইন অনুযায়ী আমাদের...”
“আপনারা কর্ণেল সারটোরিসের সঙ্গে কথা বলুন,” এমিলি শুকনো স্বরে বললেন। (যদিও কর্ণেল সারটোরিস দশ বছর আগেই মারা গেছেন।)
“জেফারসনে আমি ট্যাক্স দিই না।”
“টোবে!” মুহূর্তেই নিগ্রো চাকরটি এগিয়ে এলো, “এঁদের বাইরে নিয়ে যাও।”
কমিশনাররা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেন। তিরিশ বছর আগে, যখন মিস এমিলির বাড়ি থেকে অদ্ভুত দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল, তখনও এঁদের পূর্ব পুরুষেরা একইভাবে হেরে গিয়েছিলেন। তার দুই বছর আগে এমিলির বাবা মারা যান, আর কিছুদিন আগেই এমিলির প্রেমিক হোমার ব্যারন তাকে ছেড়ে চলে যান। অথচ আমরা সবাই ভেবেছিলাম, হোমার ব্যারনের সঙ্গেই এমিলির বিয়ে হবে।
বাবার মৃত্যুর পর মিস এমিলি খুব কমই বাড়ির বাইরে বের হতেন। আর যেদিন হোমার ব্যারন তাকে ছেড়ে চলে গেল, এমিলি যেন পুরোপুরি অন্তরালে চলে গেলেন। কেউ কেউ সাহস করে দেখা করতে গেলেও, এমিলি কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। বাড়ির একমাত্র জীবনের চিহ্ন ছিল নিগ্রো চাকর টোবে, তখনও যুবক। সে বাজারের ঝুড়ি হাতে বাইরে যেত, তারপর ফিরে এসে বাড়ির ভেতর ঢুকত।
“পুরুষ মানুষ কি আর রান্নাঘর পরিষ্কার রাখতে পারে?” মেয়েরা বলাবলি করত। তাই এমিলির বাড়ি থেকে যখন তীক্ষ্ণ দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করল, কেউ খুব অবাক হয়নি। সেই দুর্গন্ধ যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে সাধারণ জনজীবন আর অভিজাত গ্রিয়ারসন পরিবারের মধ্যে আরেকটি অদৃশ্য সংযোগ তৈরি করেছিল।
এক প্রতিবেশিনী মেয়রের কাছে অভিযোগ জানালেন। তখন শহরের মেয়র ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি ষ্টিভেনস, যাঁর বয়স ছিল আশির কাছাকাছি।
“কিন্তু ম্যাডাম, এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি?” মেয়র জিজ্ঞেস করলেন।
“কেন, মিস এমিলিকে খবর পাঠান। এভাবে আশপাশে দুর্গন্ধ ছড়ানো তো আইনবিরুদ্ধ।”
“তার দরকার হবে না। হয়তো বাড়ির আশপাশে সাপ বা ইঁদুর মেরে ফেলেছে ওই নিগ্রো চাকরটা... আমি তাকে বলব।”
কিন্তু পরদিন মেয়রের কাছে আরও কয়েকটি অভিযোগ এল। এক ভদ্রলোক, কিছুটা দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে, লিখলেন, “কিছু একটা করা দরকার। আমি মিস এমিলিকে বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু বিশ্রী গন্ধটা সহ্য করা যাচ্ছে না।”
সেদিন রাতে কমিশনারদের মিটিং বসলো—তিনজন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ এবং একজন তরুণ সদস্য। তরুণ সদস্যটি সরলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, মিস এমিলিকে বার্তা পাঠিয়ে বলা হোক যে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। “উনাকে কিছুটা সময় দিন। যদি উনি নেহাতই...”
“মাথা খারাপ নাকি মশাই?” মেয়র আঁতকে উঠে বললেন, “একজন অভিজাত পরিবারের ভদ্রমহিলাকে আপনি বলবেন যে ওঁর বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে?”
অতএব, পরের দিন মধ্যরাতে, চারজন লোক চোরের মতো মিস এমিলির লন পেরিয়ে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে লাগল। ইটের গাঁথনির নীচে ও ভাঁড়ার ঘরের কাছ থেকে কোনো বাজে গন্ধ আসছে কিনা তা শুঁকে দেখল। একজন লোক কাঁধে ঝোলানো চুনের থলি থেকে চুন ছড়াতে লাগল।
লন পেরিয়ে যখন তারা ফিরে গেল, তখন বাড়ির ওপরতলার একটি অন্ধকার জানলায় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। আলোর পেছনে দেখা গেল মিস এমিলির ঋজু, অনমনীয় শরীর—পাথরে গড়া মূর্তির মতো স্থির ও নিশ্চল। যারা বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করতে এসেছিল, তারা লুকিয়ে পড়ল রাস্তার ধারের গাছের ছায়ায়। সপ্তাহখানেক পরে বাড়ি থেকে আর কোনো দুর্গন্ধ আসেনি।
এই ঘটনার পর থেকেই জেফারসনের মানুষ মিস এমিলিকে নিয়ে এক ধরনের অনুশোচনায় ভুগছিল। কারণ এমিলির দূর সম্পর্কের দাদীমা মিসেস ওয়াট শেষ বয়সে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।
শহরের লোকের ধারণা ছিল, গ্রিয়ারসন পরিবার নিজেদের যতটা অভিজাত ভাবে, বাস্তবে তার চেয়েও বেশি ভান করত। এমিলির বাবা কখনোই শহরের কোনো যুবককে উপযুক্ত পাত্র বলে মানেননি।
অনেকেই কল্পনায় দেখেছে এক মূকাভিনয়ের নাটকীয় দৃশ্য—পেছনের মঞ্চে সাদা পোশাকে তন্বী এমিলি, আর সামনে তাঁর বাবার কুৎসিত ছায়া, হাতে চাবুক ধরা। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা, যেন কোনো অপমানিত প্রেমিক সেখান দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে।
তিরিশের কোঠায় পৌঁছেও যখন মিস এমিলির বিয়ে হল না, আমাদের মধ্যে যেন এক ধরনের অপ্রকাশিত সন্তুষ্টি কাজ করেছিল। আমরা খুশি না হলেও, গ্রিয়ারসন পরিবার নিয়ে আমাদের ধারণাটি সঠিক প্রমাণিত হল। যদিও পরিবারে পাগলামির ইতিহাস ছিল, তবু যদি সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করা যেত, এমিলির বিয়ে হতে পারত।
তার বাবা মারা যাওয়ার পর জানা গেল, বাড়িটি ছাড়া তিনি এমিলির জন্য কিছুই রেখে যাননি। একদিক থেকে লোকে খুশি হল—এমিলি এখন নিঃস্ব, একা, আমাদেরই একজন। সামাজিক রীতিনীতি মেনে মহিলারা সহানুভূতি জানাতে এমিলির কাছে গেলেন। কিন্তু এমিলি আগের মতোই ছিল—পোশাকে কোনো পরিবর্তন নেই, মুখে বিষাদের ছাপ নেই। যেন বোঝাতে চাইছিল, “আমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন।”
তিনদিন পর্যন্ত তার বাবার মৃতদেহ কবর দেওয়া গেল না। পাদ্রী ও ডাক্তার অনেক বোঝানোর পরও যখন কাজ হল না, এবং জোর করে মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল, তখন হঠাৎ ভেঙে পড়ল এমিলি। যত দ্রুত সম্ভব আমরা মৃতদেহটি গোরস্থানে নিয়ে গেলাম।
আমরা তখনও মিস এমিলিকে পাগল বলিনি। কারণ আমরা জানতাম, এটা তার জীবনের এক স্বাভাবিক পরিণতি। একের পর এক যুবক তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল, কিন্তু এমিলির বাবা সবাইকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন, যখন এমিলি একা, নিঃস্ব, অসহায়, তখন সে কার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবে? যার কারণে তার জীবনের সমস্ত সুখ ও সম্পদ হারিয়ে গেছে—তাঁকেই, তাঁর স্মৃতিকেই।
অনেক দিন অসুস্থ থাকার পর, যখন আবার এমিলিকে গির্জায় দেখতে পেলাম, সে যেন একেবারে তন্বী মেয়ের মতো হয়ে গেছে। তার চুল ছোট করে কাটা, আর ছোট জানালার রঙিন কাঁচে আঁকা দেবদূতের মতো তার মুখে শোক আর শান্তির মিশ্রণ।
এরই মধ্যে শহরের ফুটপাথ বাঁধানোর কাজ শুরু হল। এমিলির বাবার মৃত্যুর পর কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল। কাজ শুরু করল নিগ্রো শ্রমিকেরা, শুয়োরের পাল, কনস্ট্রাকশন কোম্পানির যন্ত্রপাতি এবং এক তরুণ ইয়াংকি ফোরম্যান—তার নাম হোমার ব্যারন।
হোমার ব্যারন ছিল দীর্ঘকায়, শ্যামলা রঙের, কৌশলী, দক্ষ ও উদ্যোগী এক পুরুষ। তার কণ্ঠটি ছিল দরাজ, আর চোখের মনি কালো হলেও চামড়ার মতো অত গাঢ় ছিল না। বাচ্চারা দল বেঁধে তার পেছনে হাঁটত, আর সে নিগ্রো মজুরদের ধমক দিত। তার তালে তালে মজুরেরা গাঁইতির ওঠা-নামার ছন্দে গান গাইত। পার্ক কিংবা চৌরাস্তার কাছাকাছি শহরের যেকোনো জায়গায় হাসির শব্দ শুনলে, ভীড়ের কেন্দ্রে তাকে খুঁজে পাওয়া যেত।
এক সময় দেখা গেল, প্রতি রবিবার বিকেলে হোমার ব্যারন ও মিস এমিলি হলুদ ঘোড়ায় টানা হলুদ চাকাওয়ালা বগি গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরোয়। হোমারের প্রতি এমিলির উৎসাহ দেখে আমরা খুশি হয়েছিলাম। তবে মহিলারা বলেছিলেন, গ্রিয়ারসন পরিবারের কোনো মেয়ে উত্তর রাজ্য থেকে আসা একজন ইয়াংকি দিনমজুরের সঙ্গে কখনোই গুরুতর সম্পর্কে জড়াবে না।
বয়স্করা বলতেন, দুঃখ যতই তীব্র হোক না কেন, অভিজাত পরিবারের কোনো মহিলা তার আভিজাত্যের দায়িত্ব ভুলে না। তারা কেবল আফসোস করে বলত, “বেচারা এমিলি, তার আত্মীয়দের উচিত তাকে বোঝানো।”
তবু রবিবার বিকেলগুলোতে হলুদ ঘোড়ায় টানা হলুদ চাকাওয়ালা বগি গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলত। আশপাশের বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ থাকত, যেন সূর্যের আলো ভেতরে না ঢোকে। খড়খড়ির আড়ালে রেশম ও সাটিন কাপড়ের শব্দ শোনা যেত, আর লোকেরা বলত, “বেচারা এমিলি...”
তবে এমিলি মাথা উঁচু করে চলাফেরা করত। আমরা তখনই হয়তো তার নৈতিক পতনের কথা ভাবতাম। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হতো, গ্রিয়ারসন পরিবারের শেষ প্রতিনিধি আমাদের কাছ থেকে তার আভিজাত্যের স্বীকৃতি চাইছে। যেন পৃথিবীর মাটির সঙ্গে তার এই নতুন সংযোগ আরও একবার প্রমাণ করছিল যে, প্রকৃত আভিজাত্যের চিহ্ন হলো কোনো কিছুতে বিচলিত বা প্রভাবিত না হওয়ার ক্ষমতা।
একবার এমিলি ইঁদুর মারার বিষ কিনতে গিয়েছিলেন—ঘটনাটা এক বছর পরের। সে সময় শহরের সবাই বলাবলি করছিল, “বেচারা এমিলি,” কারণ তখন অ্যালাবামা থেকে তার দুজন মামাতো দিদি এসে তার সঙ্গে দেখা করছিলেন।
ওষুধের দোকানে ঢুকে এমিলি সেলসম্যানকে বলেছিলেন, “আমি বিষ কিনতে চাই।” তখন তার বয়স তিরিশের একটু বেশি। আগের চেয়ে আরও শুকনো, মাথার রগ আর চোখের কোটরের চারপাশে চামড়া টানটান। তার দৃষ্টি শীতল, উদ্ধত—যেন লাইটহাউসের আলো, যা নাবিককে রাতের সমুদ্রে পথ দেখায়।
“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু, মিস এমিলি, আপনি কোন ধরনের বিষ চান? ইঁদুর মারার জন্য?” সেলসম্যান জিজ্ঞেস করেছিলেন।
“তোমার দোকানের সবচেয়ে ভালো বিষটাই দাও। কোন ধরনের সেটা, তাতে আমার কিছু যায় আসে না,” দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন এমিলি।
দোকানদার বেশ কয়েকটি বিষের নাম বললেন।
“এগুলো হাতি মারার জন্যও যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যা চাইছেন, তা হলো আর্সেনিক। বিষটা খুবই শক্তিশালী নয়?”
“আর্সেনিক? হ্যাঁ, ম্যাডাম। কিন্তু আপনি এটা কেন চাইছেন?”
“আমি আর্সেনিক চাইছি,” দৃঢ় কণ্ঠে বললেন এমিলি।
দোকানদার তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমিলি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন। তার শিরদাঁড়া সোজা, মুখের চামড়া যেন বাতাসে উড়ন্ত নিশানের মতো টান টান।
“কিন্তু ম্যাডাম, আইন অনুযায়ী আপনাকে বলতে হবে, এই বিষ কেনার উদ্দেশ্য কী?”
এমিলি মাথা সামান্য পিছনে ঝুঁকিয়ে বিস্ফারিত চোখে দোকানদারের দিকে তাকালেন। চোখে চোখ পড়ল, তারপর দোকানদার চোখ নামিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।
দোকানদার আর্সেনিক প্যাকেটে মুড়ে দিলেন। নিগ্রো ডেলিভারি-বয় সেই প্যাকেট এমিলির হাতে পৌঁছে দিল, কিন্তু দোকানদার আর কখনও আসেননি।
বাড়ি ফিরে এমিলি প্যাকেট খুললেন। বাক্সের ওপরে মড়ার খুলি ও হাড়ের চিহ্ন আঁকা ছিল, আর নীচে লেখা:“ইঁদুরের জন্য।”
পরের দিন আমরা সবাই বলেছিলাম, এমিলি আত্মহত্যা করবে। এবং মনে হয়েছিল, সেটাই ভালো।
প্রথমবার যখন হোমার ব্যারনের পাশে এমিলিকে দেখেছিলাম, তখন বলেছিলাম, তারা বিয়ে করবে। কিন্তু পরে শুনলাম, এক্স ক্লাবের ছোকরাদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে হোমার বলেছে, বিয়ে করা তার ধাতে নেই। তবু আমরা ভেবেছিলাম, এমিলি তাকে বিয়েতে রাজি করাতে পারবে।
তারপর প্রতি রবিবার আমরা বন্ধ খড়খড়ির আড়াল থেকে তাকিয়ে বলতাম, “বেচারা এমিলি।” রাস্তা দিয়ে ছুটে যেত হলুদ চাকাওয়ালা বগি গাড়ি। এমিলি মাথা উঁচু করে বসে থাকত, আর হোমার ব্যারন, মাথায় হ্যাট ট্যাড়া লাগানো, দাঁতের ফাঁকে সিগার, হাতে হলুদ দস্তানায় ধরা ঘোড়ার লাগাম আর চাবুক নিয়ে, যেন এক বিজয়ী পুরুষের মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে গাড়ি চালাত।
এরপর মহিলারা বলতে শুরু করলেন, এমিলির এই আচরণ শহরের মান-মর্যাদা ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে, আর ছেলে ছোকরাদের জন্যও এটি খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত। পুরুষদের কেউই এমিলির ব্যাপারে মাথা গলাতে চাননি, কিন্তু মহিলাদের চাপে পড়ে পাদ্রী এমিলির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।
পাদ্রী সেই সাক্ষাতে কী ঘটেছিল তা কখনও বলেননি, তবে আর কখনোই তিনি এমিলির সঙ্গে দেখা করেননি। পরের রবিবার আবার এমিলি ও হোমার বগি গাড়ি হাঁকিয়ে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।
অগত্যা, মহিলারা অ্যালাবামায় এমিলির আত্মীয়দের চিঠি লিখলেন। শেষমেশ তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা এসে হাজির হল। “এবার কী হয় দেখা যাক,” আমরা ভাবছিলাম।
প্রথমে কিছুই ঘটল না। পরে আমরা নিশ্চিত হলাম, এমিলি ও হোমারের বিয়ে হতে চলেছে। কারণ, এমিলি গয়নার দোকানে পুরুষদের জন্য রূপোর তৈরি টয়লেট সেটের অর্ডার দিয়েছেন। প্রত্যেকটি জিনিসে খোদাই করা থাকবে হোমার ব্যারনের নামের আদ্যাক্ষর—এইচ. বি.
কিছুদিন পর আমরা শুনলাম, এমিলি নাইট শার্টসহ একটি পুরুষের পোশাকের সম্পূর্ণ সেট কিনেছেন। এতে আমাদের ধারণা হলো, বিয়ের সব আয়োজনই ঠিকঠাক চলছে। আমরা খুশি হলাম।
এদিকে, রাস্তা বাঁধানোর কাজও শেষ হয়ে গেছে। তাই যখন হোমার ব্যারন হঠাৎ একদিন শহর থেকে উধাও হয়ে গেল, আমরা খুব একটা অবাক হলাম না।
আমরা ভাবলাম, হয়তো সে বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত, অথবা এমিলির মামাতো বোনেরা অ্যালাবামায় ফিরে যাওয়ার পরই সে আবার ফিরে আসবে।
এক সপ্তাহ পরেই এমিলির মামাতো বোনেরা অ্যালাবামায় ফিরে গেল। আর ঠিক তিন দিন পর শহরে ফিরে এলেন হোমার ব্যারন। সন্ধ্যায় একজন প্রতিবেশী দেখেছিলেন, নিগ্রো চাকর পেছনের দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিল।
কিন্তু এরপর আর কখনো আমরা হোমার ব্যারনকে দেখিনি। এমিলি নিজেও কিছুদিনের জন্য যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাড়ির ভেতরে শুধু নিগ্রো চাকর বাজারের ঝুড়ি নিয়ে আসা-যাওয়া করত। সামনের দরজাটি সবসময় বন্ধ থাকত।
কখনো কখনো এমিলিকে জানালায় দেখা যেত, যেমন সেদিন রাতে, যখন পৌর কর্মীরা দুর্গন্ধ দূর করতে বাড়ির আশেপাশে চুন ছড়াচ্ছিল। কিন্তু তারপরের দুই মাস এমিলি আর রাস্তায় বের হননি। আমরা জানতাম, এটি এমিলির স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায়।
তার বাবার সেই দহনশীল, তীব্র গুণের উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন, যা তার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেই আগুনের ক্রুদ্ধ শিখা, যা এত বছর পরেও নেভেনি।
আবার যখন এমিলিকে দেখলাম, সে মোটা হয়ে গেছে এবং তার চুলে পাক ধরেছে। পরবর্তী কয়েক বছরে তার চুল আরও পেকে নুন মেশানো গোলমরিচের গুঁড়োর মতো রং ধরল, যা শেষে লোহার চূর্ণ ধূসর রঙে পরিণত হলো। তখন তার চেহারা যেন একজন পরিশ্রমী ও শক্তিশালী প্রৌঢ় পুরুষের মতো। যখন চুয়াত্তর বছরে এমিলি মারা গেলেন, তার চুল ঠিক সেই ধূসর রঙেই রয়ে গিয়েছিল।
এই সময় থেকেই সামনের দরজাটি প্রায়ই বন্ধ থাকত। মাঝখানে ছয়-সাত বছর, এমিলি নিচতলার একটি ঘরে স্টুডিও সাজিয়ে চীনা মাটির উপর ছবি আঁকার ক্লাস চালাতেন। তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ। কর্ণেল সারটোরিস ও তার বন্ধুদের মেয়ে এবং নাতনীদের সেখানে পাঠানো হতো, ঠিক সেই একই কর্তব্যবোধ থেকে, যার জন্য তাদের পঁচিশ সেন্টের মুদ্রা হাতে নিয়ে রবিবার গির্জায় পাঠানো হতো।
এরই মধ্যে এমিলির ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছিল।
তারপর এলো নতুন যুগ, নতুন মানুষ। তারা শহরের নতুন প্রজন্ম, যাদের কাঁধে ভর করেই শহরের উন্নতি চলতে থাকে। যে মেয়েরা একসময় চীনামাটির উপর ছবি আঁকার ক্লাস করেছিল, তারা তখন মা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের মেয়েদের আর কেউ রঙের বাক্স, তুলি কিংবা ম্যাগাজিনের কাটা ছবি নিয়ে এমিলির কাছে পাঠায়নি।
শেষ ছাত্রী বিদায় নেওয়ার পর সামনের দরজাটি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।
দিন, মাস, বছর পেরিয়ে গেল। নিগ্রো চাকরের চুল পেকে গেল, শরীর কুঁজো হয়ে পড়ল। তবে এখনও সে বাজারের ঝুড়ি হাতে বাইরে যায় এবং ভেতরে ফিরে আসে। মাঝেমধ্যে নীচতলার একটি জানালায় এমিলিকে দেখা যায়। ওপরতলাটা হয়তো সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছেন তিনি।
যেন দেয়ালের ছোট খোপে রাখা পাথরের মূর্তি—নিথর, শীতল। সে আমাদের দিকে চেয়ে আছে কি না, তা কেউ বলতে পারে না। এমিলি এভাবেই যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিলেন—শহরের প্রিয়, অথচ রহস্যময় রমণী। তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু কোনো কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না। শান্ত, নিথর, মনোবিকারের প্রতিচ্ছবি হয়ে তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন।
অবশেষে একদিন এমিলি মারা গেলেন। ধুলো আর ছায়ায় ঢাকা বাড়ির ভেতরে, অসুস্থ অবস্থায়, তার পাশে শুধু ছিল নিগ্রো চাকর। আমরা জানতাম না তিনি অসুস্থ। চাকরও কারো সঙ্গে কথা বলত না, হয়তো এমিলির সঙ্গেও নয়। তার কণ্ঠস্বর দীর্ঘ নীরবতায় যেন মরচে পড়েছিল।
নীচতলার একটি ঘরে তিনি মারা গেলেন। ওয়ালনাটের ভারী খাটে, পর্দার আড়ালে শুয়ে থাকা মাথাটি, যা পাকা চুলে ঢাকা, বালিশের ওপরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আলোর অভাবে তার চারপাশে একটি হলদে ছাপ পড়ে গিয়েছিল।
যে মহিলারা প্রথমে এসেছিলেন, নিগ্রো চাকরটি তাদের জন্য দরজা খুলে দিল। মহিলারা চাপা গলায় কথা বলছিলেন, তাদের দ্রুত ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ঘরের চারপাশে ঘুরছিল। নিগ্রো চাকরটি বাড়ির ভেতরে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর তাকে এই শহরে আর কখনও দেখা যায়নি।
অ্যালাবামা থেকে এমিলির দুই মামাতো বোন এসেছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হল। বাজার থেকে কেনা ফুলের স্তবকের আড়ালে লুকিয়ে গেল এমিলির দেহ। ঘরে ছিল তার বাবার পুরনো পেন্সিলে আঁকা ছবি—মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিত। মহিলাদের কলরব অদ্ভুতভাবে জোরাল আর বিক্ষিপ্ত শোনাচ্ছিল।
কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ, যারা আজ কনফেডারেট সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ব্রাশ করে পরে এসেছে, লন আর বারান্দায় ভিড় জমিয়ে মিস এমিলির গল্প করছিল। তাদের গল্প শুনলে মনে হবে, তারা মিস এমিলির সমবয়সী। হয়তো তারা সত্যিই বিশ্বাস করত যে, তারা যৌবনে এমিলির সঙ্গে পার্টিতে নেচেছিল কিংবা তাকে ভালোবেসেছিল।
তাদের স্মৃতিতে সময় যেন কোনো সরল গণিতের নিয়ম মানে না। অতীত তাদের স্নায়ুতে ক্ষীয়মান কোনো পথ নয়, বরং এক বিশাল প্রান্তর, যা শীতের হিমতুষারও সম্পূর্ণ স্পর্শ করতে পারে না। তাদের কাছে বর্তমান যুগ যেন একটি বোতলের সরু মুখ, যা তাদের বিস্তৃত অতীতের মাঝে একটি ক্ষীণ ব্যবধান তৈরি করে।
আমরা জানতাম, বাড়ির ওপরতলায় একটি ঘর আছে, যেখানে গত চল্লিশ বছর ধরে কেউ পা রাখেনি। প্রয়োজনে দরজা ভেঙে সেখানে ঢুকতে হবে, সেটাও আমাদের জানা ছিল।
আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, যতক্ষণ না মিস এমিলির মৃতদেহ যথাযথ সম্মানে কবরস্থ হয়।
অবশেষে দরজা ভাঙা হলো। প্রচণ্ড আলোড়নে ঘর ধুলোর মেঘে ঢেকে গেল। একটি ক্ষীণ, তীক্ষ্ণ গন্ধ আমাদের নাকে ভেসে এল, যেন আমরা কোনো কবরের ভেতরে প্রবেশ করেছি।
ঘরটি নববধূর বাসর শয্যার জন্য সাজানো ছিল। পর্দায় ঝরা গোলাপের রঙ ছড়ানো, আলোয় গোলাপি শেড। কিন্তু সবকিছু থেকে কবরের সেই তীক্ষ্ণ গন্ধ ভেসে আসছিল। ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ফটিকের পানপাত্র, জং ধরা রূপোর তৈরি পুরুষের টয়লেট সেট—সবকিছুতেই সেই গন্ধ। রূপোর সেট এত কালো দাগে ভরা যে, খোদাই করা নামের আদ্যাক্ষরগুলো আর বোঝা যায় না।
ঘরের জিনিসপত্রের ভিড়ে একটি কলার আর টাই এমনভাবে পড়ে ছিল, যেন কেউ সেগুলো হঠাৎ খুলে রেখে গেছে। ধুলোর ওপরে আধো চাঁদের মতো দাগ স্পষ্ট। চেয়ারের পেছনে সযত্নে ভাজ করা শ্যুট, নীচে এক জোড়া জুতো-মোজা—নীরব, পরিত্যক্ত।
আর বিছানার ওপরে শুয়ে ছিল একজন পুরুষ!
আমরা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম, শুধুই দেখছিলাম। বিছানায় শুয়ে থাকা মাংসহীন মুখে ছিল এক অদ্ভুত গম্ভীর হাসি। তার শরীরের অবস্থান দেখে বোঝা গেল, একসময় সে কাউকে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু এখন, যে দীর্ঘ নীরব ঘুম প্রেম এবং মিলনের ক্ষণিক মুখভঙ্গিমাও মুছে দেয়, সেই ঘুমে সে তার প্রেমিকার কাছে প্রতারিত হয়েছে।
তার যা কিছু অবশিষ্ট, নাইট শার্টে যা এখনও টিকে আছে, সবই পচাগলা শবদেহে মিশে গেছে। শরীর আর বিছানাকে আলাদা করা যায় না। তার শবদেহ এবং মাথার নিচের বালিশ ধুলোর স্তরে ঢাকা পড়েছে। সেই ধুলো, যা কখনো ধৈর্য হারায় না, চিরকাল নিঃশব্দে জেগে থাকে।
তারপর আমরা দেখতে পেলাম, বিছানায় আরেকটি বালিশে কারো মাথার চিহ্ন। যেন কেউ শবদেহের পাশে শুয়ে থেকেছে। আমাদের একজন সেই বালিশ থেকে কিছু তুলে নিল।
প্রায়-অদৃশ্য ধুলোর কটুগন্ধের মধ্যে আমরা দেখলাম একগাছি পাকা চুল। মেয়েলি মাথার চুল, যার রং ছিল চূর্ণ লোহার মতো ধূসর।





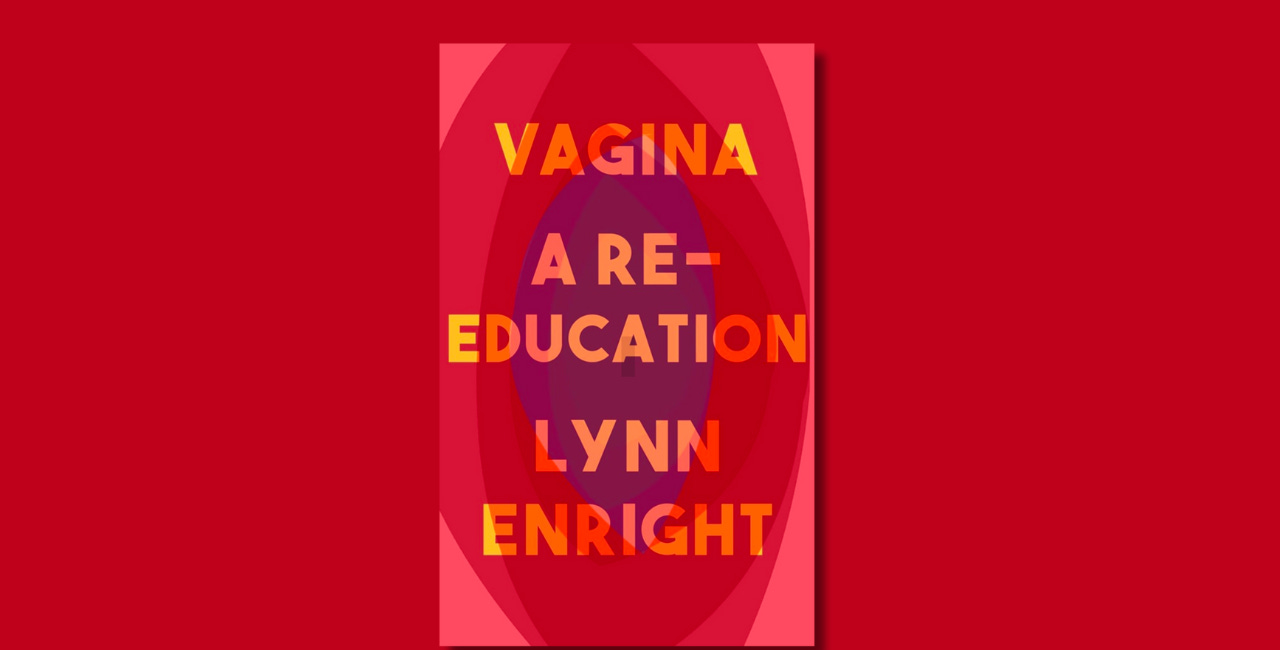

Lucid and fluent. ঝরঝরে, মেদহীণ,সাবলীল এরকম অনুবাদ অনেক দিন পড়িনি।