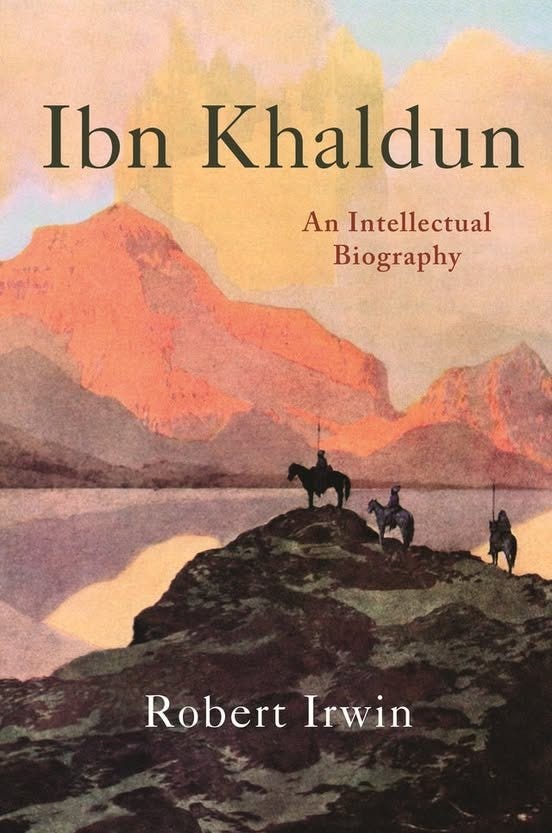ক্ষমতার চিরন্তন চক্র: ইবন খালদুন ও ইতিহাসের দর্শন
সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার উত্থান-পতনের অন্তর্নিহিত সূত্রের অনুসন্ধান
ইবন খালদুনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব আজকের পৃথিবীতে এমন এক বিস্তৃত মহাসাগর, যেখানে এঙ্গেলস থেকে রিগান, টয়নবি থেকে তামবুররলেন সবাই কোনো না কোনোভাবে তাঁর চিন্তার ঢেউয়ের সংস্পর্শে এসেছেন। অথচ আরবি ভাষাভাষী জগতে তাঁর চিন্তার যথাযথ মূল্যায়ন আজও হয়নি, বরং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কখনো কখনো তাঁকে ওরিয়েন্টালিস্ট বলেও চালানো…